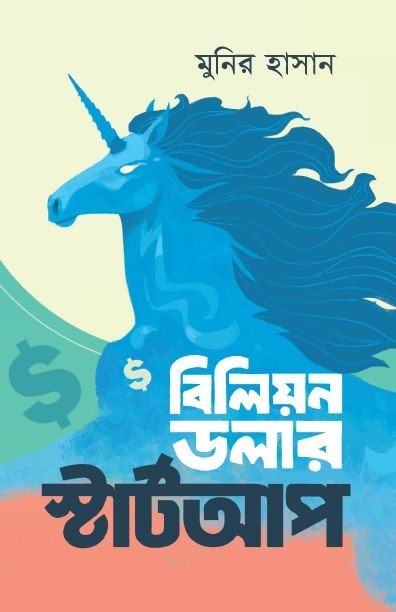পড়, পড়, পড় – ১০ পর্ব একসঙ্গে
১.
১৯৮৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। ট্রেনে করে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এসেছি। একটা বড় ব্যাগ (স্যুটকেস না), একটা তোষক, একটা মশারী, একটা বালিশ। সঙ্গে মা। মা’কে খালার বাড়িতে রেখে বিকেলে এসে হাজির হলাম বুয়েটের আহসানউল্লাহ হলে। দুইটি ছাত্র সংগঠনের চিঠি পেয়েছি আর প্রভোস্ট-এর একটা। কাজে নিশ্চিত ছিলাম যে একটা কোন অভ্যর্থনা থাকবে। কিন্তু হা, হতোম্ভি। দারোয়ান চাচা অবাক হয়ে জানতে চাইল – আপনি তোষক টোষক আনছেন ক্যান? আজকে তো কোন রুম দেওয়া হবে না। আর প্রভোস্ট স্যার তো আসেন সন্ধ্যা বেলায়। অফিসও তখন খুলবে। কী মুশকিল! খালার বাসায় যাবো? মা’কে যে বড় গলায় বলে আসলাম হলে থাকতে যাচ্ছি! যাকগে, দারোয়ান চাচাকে বললাম যেহেতু ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে দৌড় ঝাপ করা সম্ভব না। কাজে এগুলো আপনার রুমে থাক। সন্ধ্যায় দেখা যাবে।
সন্ধ্যা বেলায় দেখলাম আরো অনেকে হাজির। ফরম ফিলাপ করে বসে থাকলাম। এর মধ্যে হলের কেয়ারটেকারের সঙ্গে আলাপ। খুবই অবাক কারণ ঢাকা শহরে থাকার কেও নাই এমন কী হলেও থাকতে পারি এমন কাউকে আমি চিনি না!!! কেমিস্ট্রির মনোয়ার স্যার (নাম পরে জেনেছি), সহকারি প্রভোস্ট। আমার ইন্টারভিউ নিলেন। বললেন – ঠিক আছে, আজকে যাও। পরশু দিন আমরা যাদের সিট দেওয়া হবে তাদের নাম টাঙ্গিয়ে দেব। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠি না।
-এই ছেলে। এবার যাও। পরশু দিন আসবা।
– স্যার, আমি কই যাবো? কোথায় যাবো?
– কোথায় যাবা মানে কী? তুমি চট্টগ্রাম থেকে কখন আসছো, ঢাকায় কে আছে?
– ট্রেনে এসে দুপুরে পৌছেছি। ঢাকায় কেও নাই।
-কেও নাই মানে? ব্যাগ ট্যাগ কই।
-কমলাপুর থেকে সরাসরি ওখানে এসেছি। ব্যাগ-তোষক দারোয়ান চাচার রুমে।
হতভম্ব স্যার বেল বাজিয়ে কেয়ারটেকারকে ডাকলেন। জাফর সাহেব (নাম পরে জেনেছি) জানালেন – জি, ওনার ব্যাগ তোষক দারোয়ানের রুমে আছে। দারোয়ানকে ডাকা হল কেন আমার ব্যাগ ট্যাগ রাখছে। বেচারা।
– ঠিক আছে। দেখি আমি কী করতে পারি। পাশের রুমে গিয়ে বসে থাকো।
তো, আমি বসে আছি। ভাবছি রাতের দিকে যদি ছেড়ে দেয় কই যাবো? ঢাকা শহরতো সেভাবে চিনি না। খালাম্মার বাসায় যাওয়া যাবে কিন্তু প্রেস্টিজতো থাকবে না!!!
রাত ৯টার দিকে স্যার আমাকে ডাকলেন। আরো কী কী প্রশ্ন করলেন। মনে নাই।
টাকা পয়সা আছে কী না জানতে চাইলেন। বললাম – আছে। ফী টী এসব নিয়ে এসেছি। তারপর বললেন – তোমাকে একটা টেম্পোরারি রুম দেওয়া হল। সেখানে তুমি থাকবা। কিন্তু পরে যদি মেরিটে সিট না পাও তাহলে তোমাকে আমি রাখতে পারবো না।
-হলে সিট না পেলে আমার আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হবে না। আমি বাড়ি চলে যাবো।
জাফর সাহেব, আমাকে নিয়ে গেলেন আহসানউল্লাহ হলের নতুন চারতলায়। ৪১৫ নম্বর রুমটি আমাকে খুলে দেওয়া হল। আমি ঐ রুমের প্রথম বাসিন্দা। কারণ ঐ ফ্লোরটি এবারই হয়েছে। জানলাম নতুন একটা জীবন শুরু হবে। পরের দিনের পরের দিন থেকে শুরু হয়ে গেল বুয়েট জীবন। সুন্দর এবং সোনালী। আনন্দেরও। সম্ভবত জীবনের অন্যতম সুন্দর একটা চ্যাপ্টার।
তবে, এটা হল উপক্রমনিকা।
কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম হিসাবে কিছুটা গোলমাল হয়েছে। কারণ মাসে মিল চার্জ ২৭০ টাকা। বাবা পাঠাবেন মোট ৭০০ টাকা। এই দিয়ে তিনবেলা নাস্তা, রিকশা ভাড়া, খাতা-কলম কেমনে কী? তার ওপর রুমে একটা পত্রিকাও রাখতে চাই! কিন্তু বাবাকে টাকার কথা বলি কেমনে। কাজে খরচ কমাতে হবে। শুরু করলাম হাটা। হল থেকে গুলিস্তান হয়ে স্টেডিয়াম। হাটো।
হল থেকে বের হয়ে এসএমহলকে বামে রেখে শামসুন নাহার হল আর উদয়ন স্কুলের মাঝখানের মেঠোপথ দিয়ে টিএসসি হয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতরদিয়ে আইইবি। হাটো।
আইইবি পার হয়ে রমনা পার্কের ভেতর দিয়ে সুগন্ধা হয়ে বেইলী রোডে খালার বাড়ি। হাটো।
নিউমার্কেট হয়ে সায়েন্স ল্যাবরেটরি। ওখানে একটা সাদা বিল্ডিং-এর তিন তলায় একটা লাইব্রেরি। ওখানে ফিজিক্স টু ডে পড়া যায়! এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নাড়াচাড়া করলে কেও বকা দেয় না! হাটো।
টিএসসি হয়ে শাহবাগ হয়ে ১৪ ময়মনসিংহ রোড। বাংলা মোটর। হাটো। ওখানে একটা লাইব্রেরি আছে। অনেক বই। চট্টগ্রামে এমন কোন লাইব্রেরি নাই। খোঁজ নিয়ে জানলাম ৩০০ টাকা জমা দিলে মাসে ১০টা ফী দিয়ে প্রতিদিন ২টা বই নেওয়া যাবে।
৩০০ টাকা অনেক টাকা। একমাস চকলেট দুধ না খেলে আর সকালের নাস্তার ডিমটা বাদ দিলে শ দেড়েক টাকা বাচানো যাবে আর কয়েক দফা তিনদিনের জন্য মিল বন্ধ করে হেটে খালার বাড়িতে গিয়ে একবেলা করে খেলে ঐ টাকাটা হয়ে যাবে। তো, হোক। কিছুদিনের মধ্যে ৩১০ টাকা নিয়ে হাজির হলাম ছোট্ট বাড়িটাতে। প্রথমদিন সমরেশ বসুর একটা বই নিয়ে ফিরলাম। তারপর থেকে আামার রুটিন হয়ে গেল প্রতিদিন বিকেলে হাটতে হাটতে ঐ বাড়িটাতে যাওয়া। তখন দেশ পত্রিকায় লোটাকম্বল আর পূর্বপশ্চিম ছাপা হচ্ছে। কাজেই সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকা পড়া, পারলে একটা উপন্যাসও পড়া যায়। শুনেছি ওখানকার সিঙ্গারা অনেক মজা। কিন্তু, হেটে আসি হেটি যাই। ৩০০ টাকার কস্ট লাঘবে অনেক সময় লাগবে। কাজে শুনে শুনে সিঙ্গারা খাওয়া হয়ে যায়। কয়েকদিনের মধ্যে বুঝলাম বিক্ষিপ্তভাবে পড়লে হবে না। যে কোন এক তাক থেকে শুরু করতে হবে। কাজে একদিন সকালে ১নং দেরাজ/বইয়ের রেক-এর সবচেয়ে উপরের তাকের দুইটা বই দিয়ে নতুন করে শুরু করলাম। উদ্দেশ্য মহৎ। কত কম সময়ের মধ্যে ৩০০ টাকা উদ্ধার করা যায়!
২.
১৫ ফ্রেব্রুয়ারি রাতের বেলায় আহসানউল্লাহ হলের ৪১৫ নম্বর রুমের রাস্তার পাশের খাটটাতে মশারী টাঙ্গানোর চেষ্টা করছি। কেয়ারটেকার জাফর সাহেব আমার খোঁজ নেওয়ার জন্য পিওন একজনকে পাঠিয়েছেন এবং তার সহায়তায় আমি মোটামুটি ঘুমের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বো।
তবে তার আগে হলের সিড়ির গোড়াতে একটা কয়েন ফোন থেকে খালার বাসায় ফোন করে মাকে জানিয়েছি – বিশাল হল মা। আমাকে একটা রুমে থাকতে দেওয়া হয়েছে। একাই একটা রুম। তিনটা খাট আছে আর মানুষ আমি একলা।
দরজা বন্ধ করে বাতি নিভাবো কি নিভাবো না এমনটা ভাবছি। পরে ভাবলাম থাক, একা একা এই বিরানভুমিতে থাকবো, বাতি বরং জ্বলুক।
কতক্ষণ হল বলতে পারি না। দরজায় জোরে জোরে বাড়ি শুনে থতমত খেয়ে দেখি কেয়ারটেকারের গলা। দরজা খুলে দেখলাম আরো একজন তোষক, লেপ (আমি লেপ আনি নাই, এ দেখি এনেছে), স্যুটকেস সমেত দরজার সামনে। বুঝলাম আমার মত একই অবস্থা। কেয়ারটেকার বলে গেলেন আপনারা দুইজন এই রুমে থাকবেন। বলে তিনি চলে গেলেন।
-আমি তুহিন। মেকানিক্যাল। বলে নতুন আগন্তুক তার বাক্স পেটরা খুলে বই পত্র বের করে ফেললো। আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। এই বেটা দেখি অনেক স্মার্ট। বই কোনটা জানে!!! ভাবলাম তার কাছ থেকে জানা যাক। যা শুনলাম তাতে কিছুক্ষণ আমার কোন কথায় সরলো না।
আমার নতুন রুমমেট জানালো – বুয়েটে এই তার দ্বিতীয়বার ভর্তি হওয়া, মানে সে আমার এক ব্যাচ সিনিয়র। কিন্তু মেটালার্জি পেয়েছে বলে কিছুদিন পর আর পড়ে নাই। এবার মেকানিক্যাল পেয়েছে (পারলে আমাকে তুই বলে। দয়া করে তুমি বলছে)।
এটুকুতে আমি আসলে বোবা হইনি। হয়েছি পরের অংশ শুনে – “আমার বাসা মিরপুরে। কিন্তু এমনভাবে স্যারকে বলেছি যে ঢাকায় আমার কেও নাই। স্যার শেষ পর্যন্ত যখন আমাকে রুম দিতে রাজী হলেন তখন আমি বাসায় গিয়ে বাক্স-পেটরা নিয়ে এসেছি। কেয়ার-টেকারকে বলছি যে আমি খেয়ে আসার সময় তিতুমীর হলের ওখান থেকে আমার বাক্স প্যাটরা আনবো!!!
আমি আর কী বলবো। এসেছি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্রাম থেকে। বিদ্যা-বুদ্ধি তেমন নেই। এমন বুদ্ধিও নাই। তারপর তোষক পাততে পাততে তুহিন জানালো তার একটা কোচিং সেন্টার আছে। কয়েকটা গাইড বই বের করেছে। আগামী বছর বুয়েট ভর্তির কোচিং শুরু করবে। এগুলো বাসা থেকে করা কঠিন। সেজন্য তার হলে সিট দরকার।
আমার তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি অবস্থা। খালি মনে মনে বলি- এর সঙ্গে যদি আমার একই রুমে চার বছর থাকতে হয় তাহলে তো ও আমাকে সকালে পলাশীতে বিক্রি করে দেবে আর রাতে আবার গুলিস্তান থেকে কিনে হলে নিয়ে আসবে!!! (তুহিন অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমার রুমমেট হয়নি। মাসখানেক পর জানালো সে ট্রান্সফার নিয়ে রশীদ হলে চলে যাবে কারণ ওখানে ওর ঢাকার স্মার্ট বন্ধুরা থাকে। গ্রামের লোকজনকে ওর পছন্দ না।)
কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের রুম এলটমেন্ট হল। আমি পেলাম ১২৭ নম্বর রুম। বাথরুমের পাশের রুম। রুমমেট সিভিলের রহমতউল্লা রুপু আর একজন অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন স্মার্ট, সিভিলের। নাম মনে নেই। কেবল মনে আছে সে আওয়ামী লীগের নেত্রী বেগম সাজেদা চৌধুরীর ভাইপো! দুজনই ব্যাপক পড়ুয়া। এবং রুমে এসে দেখলাম দুজনই বই পত্র কিনে আনছে।
ওরিয়েন্টেশনে কী হল মনে নাই তেমন খালি মনে আছে কয়েক গ্রুপে ভাগ করে একজন করে লেকচারার সঙ্গে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পাস ঘুরে দেখানো হল। আমাদের দেখানো হল ওল্ড একাডেমিক বিল্ডিং। বলা হল যদিও তোমরা ইলেকট্রিক্যালের ছাত্র, কিন্তু তোমাদের বেশিরভাগ ক্লাস হবে এই পুরাতন একাডেমিক ভবনে। তারপর দেখানো হল সিভিল বিল্ডিং। নিচতলার একটা ল্যাব দেখানো হল। শপগুলো দেখানো হল। তারপর নেওয়া হল একটা কাঁচের ঘরের সামনে। সেখানে গিয়ে দেখলাম ঐ রুমের ফ্লোরের ওপর উচু করে কাঠের পাটাতন বসানো হয়েছে। কাঁচের ঘরের ভেতরে লাল লাল আলমিরার মতো কয়েকটা। তারপর চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা কিছু বাক্স। এই সময় যে লেকচারার (স্যারের নাম মনে নাই) এজন হাসিখুশী লোককে ডেকে আনলো। উনি এসে আমাদের ব্যাখ্যা করলেন – এই যে কাঁচের ঘরে যে বাক্সগুলো দেখতে পাচ্ছো এগুলো সব মিলে একটা কম্পিউটার, মেইন ফ্রেম কম্পিউটার!!! আমি খুব অবাক হয়ে দেখলাম। গ্রামের ছেলে কম্পিউটারের নাম শুনেছি কি না বলতে পারবো না। এত্তবড় একটা কম্পিউটার। লাল বাক্সগুলো আমাকে খুব আপ্লুত করলো। (পরে জানলাম ঐ লালবাক্সগুলো আসলে ছিল এয়ারকুলার!!!)।
এর মাধ্যমে আমাদের পরিদর্শন শেষ। বলা হল বিকেলে ভিসি স্যারের রিসেপশন। রশিদ বিল্ডিং এর পেছনের লনে। বিকেল চারটার সময় শুরু হবে। রুমে গেলাম। তুহিন জানালো উত্তেজনার কিছু নাই। কারণ রিসেপশনে ভিসি স্যার একটা বক্তৃতা দেবেন খালি গলায়। তারপর উনি ডিনদের সঙ্গে হাটবেন আর নাস্তা খেতে দেওয়া হবে। ওটা খেয়ে চলে আসা।
তুহিনের কথা কে পাত্তা দেয়। রিসেপশনের জন্য আগে থেকে একটা শার্ট-প্যান্ট ইস্ত্রি করে রেখেছিলাম। আমি তো জুতা পড়িনা, কী করি। তারপর ভাবলাম সবাই নিশ্চয়ই শহুরে না। আমার মত গ্রামের ছেলে-মেয়ে কয়েকজন থাকবে। তো, রিসেপশনে গিয়ে দেখলাম অনেক স্মার্ট ছেলে-মেয়ে। নিজেকে কুকড়ে একপাশে দাঁড় করিয়ে ফেললাম। ভিসি স্যার একটা বক্তৃতা দিলেন। আর সব স্যাররা (ডিনের ব্যাপারটা বুঝতাম না তখন) ঘুরতে থাকলেন। একজন শুকনা মত স্যার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ি কই। চট্টগ্রাম শুনে এক-দুই কথা বললেন। নাস্তা খাওয়ার সময় একজনকে দেখে আমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হিউবার্ট সরকার। নটরডেমিয়ান এবং ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে মেডিকেল টেস্টের সময় আর ভর্তির সময়! যাক এতক্ষণে একজনকে চিনলাম। মনটা ভাল হয়ে গেল। নাস্তা করতে করতে জানলাম হিউবার্ট হলে ওঠবে না। কারণ ওর বাসা লহ্মীবাজারে এবং সে বাসাতে থাকবে (হিউবার্ট সিভিলে পড়তো এবং তার বুয়েটে স্যার হওয়ার কথা ছিল। তবে, ফাইনাল পরীক্ষার পর স্যার হওয়ার কয়েকদিন আগে (অথবা কয়েকদিন পরে) হিউবার্ট বুড়িগঙ্গাতে ঝাপ দিল। আর উঠলো না। আমি প্রথম জানলাম কোনরকম রাজনৈতিক উত্তেজনা কিংবা প্রেমের ব্যর্থতা ছাড়াও কেবল দার্শনিক কারণে কেও একজন নিজে নিজে আত্মাহুতি দিতে পারে। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ এখন থাক)। পরের দিন প্রথম ক্লাশ। সিভিল বিল্ডিং-এ (সপ্তাহে ২ দিন সকালের দিকে সিভিল আমাদের দয়া করে তাদের বিল্ডিং-এ ক্লাস করতে দিত)। ড. আবদুর রশীদ সরকার, মেকানিক্যালের প্রথম ক্লাস। উপদশের পর তিনি যারা বোর্ডে স্ট্যান্ড করেছে তাদেরকে স্ট্যান্ড করতে বললেন। মনে হল পুরো ক্লাশই দাড়িয়ে গেল।
আমরা হাতে গোনা কয়েকজন বসে থাকলাম!
বুঝলাম ভুল জায়গায় এসে পড়েছি। কী আছে কপালে কে জানে!!!
৩.
হায়, হায় এই আমি কোথায় আসলাম।
নীলক্ষেত থেকে বই পত্র কিনলাম, কিছু পুরান বই কিনলাম। এর মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। নেমে এসেছি ১২৭ নম্বর রুমে। ক্লাসে কয়েকজন স্টারকে চিনে ফেললাম। এর মধ্যে আমাদের ব্যাচের ঢাকা বোর্ডের মেট্রিকে ফার্স্ট আশীষ কুমার কীর্তনীয়া, নটরডেমের ফার্স্ট বয় আশিকুর রহমান বিজয়, ঢাকা কলেজের ফার্স্ট বয় মাহবুব। এরকম কয়েকজন। ওদের আলাপ আলোচনা কিছুই বুঝি না।
১২৯ নম্বর রুমে আমাদের ক্লাসের একজনকে পেলাম। ক্লাস থেকে এসে কি কি জানি লেখে। রফিকুল ইসলাম। পাবনা বাড়ি। তবে, ইন্টারেস্টিংলি কয়েকজন সিনিয়রের সঙ্গে আলাপ হল। এর মধ্যে আলাপ হল ১৩৭ নম্বর রুমের অসীমদা। বিভাগ ভুলে গেছি। কিন্তু ওনাকে দেখে কিছু সাহস পেলাম। কারণ উনি দেখলাম সে অর্থে লেখাপড়া করে না। কিন্তু ফাইনাল ইয়ারে। আমি বুঝলাম যে, আমিও পাস করে যেতে পারি। একদিন তাকে সেটা বললামও যে আপনি আমার আইডল। আপনি যদি পাশ করতে পারেন আমিও নিশ্চয়ই পারবো। তিনি আমাকে আশত্ব করলেন আর নিয়ে গেলেন ১২৮ নম্বর রুমে।
ঐ রুমের একজনকে আমি দেখেছি। অনেক বয়স্ক। আমি ভেবেছি কারো চাচা-টাচা হবে। তো, অসীম দা আমাকে নিয়ে গেলেন ওনার কাছে। বললেন – মুনির আপনার পাশের রুমের নতুন বাসিন্দা, সালাম ভাই। একটু খেয়াল রাইখেন।
ভাই??
তিনি আমাকে বললেন থাকা খাওযা নিয়ে কোন অসুবিধা হলে যেন তাকে বলি। ওনার রুম থেকে বের হওয়ার পর অসীম দাকে বললাম – উনি কেন হলে থাকেন? আর কেন আপনি ওনার কাছে নিলেন?
অসীমদা জানালেন উনি যখন আহসানউল্লাহ হলে এসেছিলেন তখনও সালাম ভাই ১২৮ নম্বর কক্ষে থাকতেন। তিনি কবে বুয়েটে ভর্তি হয়েছেন সেটা কেবল উনি জানেন। এখনও তিনি থার্ড ইয়ারেই পড়েন।
“তুমিতো আমাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছ, ভাবছো না পড়েও বুয়েটে পাশ করা যায়। তা তোমার যেন চক্ষু কর্ণের বিবাদ না থাকে তাই সালাম ভাই-এর সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। (১৯৯১ সালে আমি যখন পাস করে বের হই, তখনো সালামভাই হলে থাকতেন। সম্ভবত ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সনে তিনি প্রকৌশলী হতে পেরেছিলেন।) সালাম ভাই-এর কাছ থেকে আমি জেনেছি কীভাবে রবার্ট ব্রুসের চেয়েও অধ্যবসায়ী হওয়া যায় যদিও সেটা কখনো কোন লেখক লিখেন না।
এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে। সেটা হল প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে একটা করে দলবল আসতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা কী?
অসীম দা বললেন – এটা হচ্ছে মুরগী ধরা।
– মুরগী???? মুরগী কোথা থেকে আসলো।
-আরে না ফার্স্ট ইয়ারের পোলাপাইন হল মুরগী। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এখন তাদেরকে দলে ভেড়ানোর চেস্টা করে।
– তাই নাকি? আনন্দে আমার চোখ চক চক করে উঠলো। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল জয়নাল, জাফর, মোজাম্মেল, দীপালী সাহার মুখ। মনে হল এবার আমার সামনে সুযোগ এসেছে ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থানের উত্তরাধিকার মহান ছাত্র আন্দোলনের অংশ হওয়ার!!!
এক দুইবার যে বাবার মুখটা ভাসে নাই তা না। তবে পাত্তা দিলাম না।
বলে রাখা ভাল যে, চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার সময় রাজণীতি করেছি প্রচুর কিন্তু দল করি নাই। স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে সবার আগে চলে যেতাম। তবে, কোন দলে যোগ দেইনি তখনও। ঠিক করে রেখেছিলাম ভার্সিটিতে হবে!
আমার আগ্রহ দেখে অসীমদা আমাকে একজনের কাছে নিয়ে গেলেন। সুবীরদা। সিভিলে পড়েন। অসীমদা সুধীরদাকে বললেন আমার রাজনীতির আগ্রহের কথা। আর জানালেন বুয়েটের থার্ড ইয়ার শেষে সব বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর যে পায় সে একটা এওয়ার্ড পায় (নামটা ভুলে গেছি)। ইলেকট্রিক্যালই এটা পায় কারণ আপেলের সঙ্গে তো আর আমের তুলনা হয় না। কিন্তু সুবীরদা ব্যতিক্রম। তিনি এই বছর এই পুরুস্কারটি পাচ্ছেন সিভিল থেকেই!
সুবীরদা আমার সঙ্গে অনেক আলাপ করলেন। একজন বড় ব্যক্তিত্বের কথা আসলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ইতিহাস এসবের কথাও আসলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, বুয়েটের সিভিলের রেকর্ড মার্ক নিয়ে ফার্স্ট হচ্ছে যে লোক (উনি একটা মোটাসোটা ছিলেন) সে কিনা ইতিহাসের নানান বিষয় জানে। সিরাজ সিকদারের কথা জানে। জনমানুষের অর্থনীতি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করতে পারে। দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেও নিজস্ব একটা ধারণা আছে। আর খুব পরিস্কার করে আমার মত বিশ্বাস করে – এরশাদকে সরাতে হবে। জগদ্দল পাথরের মত আমাদের ওপর চেপে বসা এরশাদকে ঠেকাতে হবে। আমি মনে মনে ভাবি যাক বুয়েটে পাশ করতে না পারি ইতিহাস নিয়ে আলাপ করার একজনকে তো পেলাম। বুয়েটে ওনার মত সবাই নিশ্চয়ই রাজনীতি সচেতন। আহা কী আনন্দ!
বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে নবীনবরণ শুরু হচ্ছে। ব্যাপক আনন্দ। এর মধ্যে তিতুমীর হলে চট্টগ্রামের কালাম ভাইরা হলে ফিরেছেন। আমি এখনো বেশিরভাগকে চিনি না। তাই সময় পেলে ওখানে চলে যাই। ওখানে একদিন লম্বা মত একজনকে দেখে মনে হল ওনাকে চিনি। উনি আমাকে ডাকলেন – ফার্স্ট ইয়ার? কোন হল।
– জি। আইসানউল্লাহ।
-কোন কলেজ?
– চট্টগ্রাম কলেজ।
– আরে ওটা তো আমারও কলেজ। আমার নাম মোজাম্মেল বাবু।
কিছুক্ষণের মধ্যে টের পেলাম উনি ব্যপক মজার মানুষ এবং গুরুত্বপূর্ণ হল তিনিও সমাজ-রাজনীতি এসব নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস থেকে শুরু করে নানান বিষয় জানেন। বিভাগ জানলাম সিভিল। আবারো হায়, হায় বুয়েটে যারা রাজনীতি সচেতন তারা সবাই সিভিল্। তার মানে মনে হয় ইলেকট্রিক্যাল পড়লে পলিটিক্স করা যাবে না। কারণ ওখানে কোন পলিটিক্যাল আলাপ নাই!!!
বেশিরভাগ ক্লাশ হয় সিভিল বা পুরাতন বিল্ডিং-এ। মাঝে মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল বিল্ডিং-এ আসি। একদিন দোতলায় এক স্যারের রুমের সামনে দেখি লেখা – আ মু জহুরুল হক!!!
আচ্ছা উনি কি সেই জহুরুল হক যিনি বিজ্ঞান সমাজ পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক লেখা লিখতেন অবাক কুতুহলে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করি? সাহস করে আমাদের ক্লাসের কয়েকজনকে, বিশেষ করে যারা ঢাকার তাদের কাছে জানতে চাইলাম?
– বিজ্ঞান সমাজ পত্রিকা???? এটা আবার কী???
কি আর করি সন্দেহ মনের মধ্যে থাকে।
এই করতে করতে ১০-১২ দিন গেল। মার্চের পয়লা সপ্তাহে শুরু হল ছাত্র সংগঠনের নবীনবরণ।
তো, এরকম একদিন রাতের বেলা রুমে বসে আছি। তখন কযেকজন আমার রুমে আসলো।
লম্বা মত একজন আমাকে বললো – মুনির, তোমাকে আমরা একটা রিকোয়েস্ট করতে এসেছি। তবে কথাটা আমি বলবো না। বলবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি এবং আহসানউল্লাহ হল শাখার সভাপতি।
– তিনি কে?
– মুনির আমি। আমি এই সংগঠনের বুয়েট শাখার সহ-সভাপতি এবং আহসান উল্লাহ হল শাখার সভাপতি।
কন্ঠ শুনেই আমার চোখ উঠেছে কপালে।
ওনার দিকে তাকিয়ে কেবল বললাম – আপনি??????
৪.
সুবীরদাকে দেখে আমি যতখানি চমকে যাই, তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হই। কারণ তাদের ব্যাচের সেরা ছাত্রটি প্রত্যক্ষ রাজনীতি করে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি আর হল শাখার সভাপতি হতে পারে, এটা দেখে আমি প্রথম বারের মত বুঝতে পারি বুয়েটে আসাটা আমার হয়তো ততটা ভুল হয়নি। তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, কালকের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে নবীনদের পক্ষ থেকে কয়েকজন বক্তৃতা দেবে। আমি যদি একজন হই তাহলে তারা খুশী হবেন। আমার জিজ্ঞাষিত নয়ন দেখে জানালেন- নবীন হিসাবে মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়ার সঙ্গে বাংলাদেশ ছাত্রলীগে যোগ দেওয়ার কোন সম্পর্ক নাই। আমি যদি যোগ দিতে না চাই তাহলে তারা আমাকে কিছুই বলবেন না।
সুবীরদা বললেন – তোমার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে তুমি রাজনীতি সচেতন, এরশাদ বিরোধী চলমান আন্দোলনের তোমার অভিজ্ঞতা আছে, কাজে তুমি যদি নবীনদের অনুভূতি প্রকাশ করো তাহলে ভাল হয়।আমিও ভাবলাম। বেশ তো।
আমি তো মনে মনে এটাই চাচ্ছিলাম। কেমন করে লাইমলাইটে আসা যায়। সারারাত নিজেকে বললাম – যা করতে হবে এক বক্তৃতায়। অন্য কোন সুযোগ পাওয়া যাবে না। কোন দিকে বক্তৃতা করলে ভাল হবে সেটা নিয়ে অনেক ভাবলাম। তবে, কোন কূল কিনারা করতে পারলাম না। কারণ কোন অভিজ্ঞতা নাই। শেষমেষ ‘যা আছে কপালে’ ভেবে ঘুমাতে গেলাম। রাতে দেখলাম হলে হলে ছাত্রলীগের নবীনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মিছিল হয়েছে। সেখানে ফার্স্ট ইয়ারেরও কয়েকজনকে দেখলাম। তবে, আমাকে কেও মিছিলে ডাকতে আসলো না। বুঝলাম দলে যোগ দেওয়া আর বক্তৃতা দেওয়া আলাদা। পরেরদিন ক্লাসে যাওয়ার সময় দেখলাম তিতুমীর হলের সামনের খোলা মাঠে প্যান্ডেল বানানো হচ্ছে। বিশাল প্যান্ডেল। অনেক উচু মঞ্চ। (এখন রাস্তার পাশে দেওয়াল আর বিভাজক আছে। সেগুলো তখন ছিল না। আর এটাই ছিল সব ধরণের মঞ্চের জায়গা। ) দেখলাম নতুনদের মধ্যে নানান আলোচনা। তবে, সবটা ঘিরে ছিল কে কে আসবে। মানে কালচারাল প্রোগ্রামে কে আসবে। সিনিয়ররা জানালো শাকিলা জাফর আর আবুল হায়াত নিশ্চিত আসবেন। আরো কে কে আসতে পারেন। তবে, আমার মাথায় ওতো চিন্তা নাই। আমি ভাবছি “আজকে ফাটায়া দিতে হবে।”
যথারীতি সন্ধ্যার পরপরই শুরু হল অনুষ্ঠান। সম্ভবত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে ওবায়দুল কাদের (ঠিক মনে নাই) এসেছিলেন এবং যথারীতি তার বক্তৃতা শুরু করেছিলেন – শুধু বিঘে দুই ছিল … বলে। আমার আগে দুইজন নবীন বক্তৃতা দিয়ে বেশ তালি টালি পেয়ে গেল। আমার নাম ধরে যখন ডাকছে তখন আমি মোটামুটি জানি কী বলবো। কিন্তু যখন মঞ্চে ডায়াসের পেছনে গিয়ে দাড়ালাম আর সামনে তাকালাম তখনই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড়। মঞ্চটা ছিল শেরেবাংলা হলের দিকে আর সামনের দিকে তিতুমির হয়ে আউল্লার সামনের রাস্তা পর্যন্ত ব্যাপক জনসমাগম (পরের কয়েকদিন অন্যান্য দলের নবীনবরনেও একই রকম সমাগম ছিল। ) মাননীয় সভাপতি বলার পরপরই আমি সব ভুলে গেলাম। কী বলবো বুঝতে না পেরে সুবীর দার দিকে তাকালাম। তিনি মঞ্চে এবং তার দিকে তাকিয়ে আমি আমার কি বলতে হবে তা বুঝতে পারলাম। সেদিন আমি যা বলেছি তার সবটা আমার মনে নাই কিন্তু একটা অংশ খুবহু মনে আছে।
আমরা যখন ভর্তি হয়ে বসে আছি, তখণ হতচ্ছাড়া এরশাদ নানান কীর্তি করে বেড়াচ্ছে। তার সর্বশেষ কীর্তি ছিল আদমজী জুট মিলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তাজুলকে হত্যা করা। তার পরে দৈনিক সংবাদে তাজুলের স্ত্রীর একটি ছবির প্রসঙ্গ তুলে তিনি তার একটা কবিতার কথা বলেন। বক্তৃতা মঞ্চে আমার এইসব কথা মনে পড়ে গেল। এবং আমি আমার কথা ফিরে পেলাম। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জয়নাল, জাফর আর মোজাম্মেলের পথ ধরেই আমাদের হাটতে হবে। এসব বলার পর আমি বললাম –আপনার জানেন, স্বৈরাচার এরশাদ কবিতা লেখে। কিন্তু ব্যাটা বাংলাও ভাল জানে না। কদিন আগে ব্যাটা বলেছে – তাজুলের স্ত্রীর ছবি দেখে বেদনায় তার মন ভরে গেছে। আমি বললাম – আরে ব্যাটা এরশাদ। তুই ব্যাটা বাংলার কী জানস। বেদনায় মানুষের মন ভরে না। বেদনায় মানুষের মন ভারাক্রান্ত হয়….
… এই অংশটুকু মনে আছে। কারণ ব্যাপক তালি পেয়েছিলাম। এবং যখন সুবীরদা মঞ্চ থেকে নামার সময় পিঠ চাপড়ে দিলেন তখন বুঝলাম আমার প্রথম কাজটা ঠিকমতোই হয়েছে।আবুল হায়াত কী এসেছিলেন, মনে করতে পারছি না। কিন্তু শাকিলা জাফর এসেছিলেন। ঐদিন জানলাম শাকিলা জাফরের স্বামী একজন প্রকৌশলী হওয়ার সুবাধে উনি ক্যাম্পাসের সবার ভাবী। অনুরোধের পর অনুরোধের পর উনি শেষ গান গাইলেন – অনেক হয়েছে, আজ যাই!!! অনুষ্ঠান শেষ একটা মধুর অনুভূতি নিয়ে আউল্লার ক্যান্টিনে গিয়ে ডিমভাজি আর পরোটা খেয়ে রুমে আসলাম। দেখলাম রুমের বাতি বন্ধ। তারমানে রুমমেটটরা কেও ফিরে নাই। দরজা খুলে বাতি জ্বালানোর পর দেখলাম মেঝের ওপর একটা ফ্লায়ার। কার্ডের ওপর ছাপানো। ওপরে বঙ্গবন্ধুর ছবি এবং জাতীয় ছাত্রলীগের নাম। ভেতরে বাম পাশে জাতীয় ছাত্রলীগে যোগ দেওয়ার আহবান এবং সেখানে সংগঠনের আদর্শ সম্পর্কে লেখা। (তখন জাতীয় ছাত্রলীগ আর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দুইটি আলাদা সংগঠন ছিল)। এগুলোই স্বাভাবিক। কাছে তেমন কোন ব্যাপার না। তবে দেখলাম ফ্লায়ারের একেবারে নিচের দিকে নবীনের কলকাকলি শিরোনামে কোটেশন মার্কের মধ্যে কিছু কথা লেখা। দেখলাম সেখানে ঐ কথাটাও আছে – আমাদের আর দাবায়া রাখতে পারবা না। কথাগুলো চেনাচেনা লাগে কারণ এই কথাগুলো আমি মোজাম্মেল বাবুর সঙ্গে কথোপকথনে বলেছিলাম। দেখলাম ঐ লেখাগুলোর নিচে নবীনের নাম আর হলের ঠিকানা দেওয়া আছে।
মুনির
১২৭ আহসানউল্লাহ হল।
৫.
এতো দেখি সর্বনাশ!
বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নবীনবরণে বক্তৃতা দিয়ে ফেলছি আর জাতীয় ছাত্রলীগের ফ্লায়ারে নিজের নাম!!! তবে, মনে মনে তো খুশী। ওরা নিশ্চয়ই এটা পুরা বুয়েটে দিয়েছে। কাছে নামতো সবাই জেনে গেছে (তখন কী জানতাম আমাদের ব্যাচেই কেবল n সংখ্যক মুনির আছে!)
তবে, কী করবো এটা নিয়ে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। পরদিন ক্যান্টিনে যাবার পথে মোজাম্মেল বাবু ভাই-এর সঙ্গে দেখা। ওনার সঙ্গে আরো একজন। মোজাম্মেল বাবু ভাই আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, মিটুন। সেই আমার আনিসুল হককে প্রথম দেখা।
আমি সাহস করে বললাম – বাবু ভাই, ফ্লায়ারে যে আমার কথাগুলো দিয়ে দিলেন। আমি তো?
– এগুলো তোমার কথা তো?
-জি। আমি আপনাকে এই কথাগুলো বলেছিলাম।
-তাইলে আর অসুবিধা কি!! নবীন বরণে থাইকো। এই বলে ওনারা চলে গেলেন। (আনিস ভাই-এর সঙ্গে আমার কোন বাক্যালাপ হয়েছে কিনা মনে করতে পারছি না। উনি যে কবিতা লেখেন এই কথাটা মনে হয় বাবু ভাই বলেছিলেন)।
অসুবিধা যে কি সেটা তো আমিও জানি না। তবে, ততোদিনে সেশনাল নামে একটা অত্যাচারের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। পরদিন সেরকম কিছু আছে ফলে এই নিয়ে বেশি ভাবার কিছু নাই।
কলেজ জীবনে ব্যবহারিক বলে একটা ব্যাপার ছিল। বুয়েটে এসে দেখলাম সেটারে বলে সেশনাল। মানে কী আল্লাহ জানে তবে পদার্থ বিজ্ঞানে দেখলাম রিপোর্ট লিখতে হয় ফিউচার টেন্সে???
প্রথমদিন যখন গিয়াসউদ্দিন স্যার বলেছিলেন যে, রিপোর্ট ঐদিনই জমা দিতে হবে তখন মনে করছি রিপোর্টে কেবল ডেটা ফেটা থাকবে। বর্ণনা লিখতে হবে না। কিনউত উনি বোঝানোর পর বুঝলাম ল্যাবের উদ্দেশ্য-বিধেয় গুলো আগেভাগে লিখে আনতে হবে। লিখতে হবে ফিউচার টেন্সে কারণ লেখা হবে আগে, পরীক্ষাটা করা হবে পরে। একটা নতুন জিনিষের নাম শিখলাম – টপশীট। মানে শাদাকাগজে রিপোর্টটা লিখতে হবে, পরে ডেটা আর রেজাল্ট যোগ করে সেটার সামনে একটা শীট যোগ করতে হবে। ঐ শীটে নাম-ধাপ ঠিকুজি লিখতে হবে। এটাকে বলা হয় টপসীট। অনেকেই দেখতাম সুন্দর করে, বিভিন্ন কালার পেন ব্যবহার করে লিখে আনে। পরে দেখলাম এই টপসীটের ব্যাপারটা সব বিষয়েই আছে!
যাকগে, ঐদিন আর একটা ছোট্ট ঘটনাও হল। চারতলায় থাকতেই হলের কমনরুমটা চিনে ফেলেছিলাম। ওখানে সবাই টেলিভিশন গিলে, টেবিল টেনিস খায় আর পত্রিকা মুখস্ত করে। কমন রুমে গিয়ে দেখলাম কয়েকটা দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক এমনকি চিত্রবাংলা নামের একটা ম্যাগাজিনও রাখা হয়। আমারে আর পায় কে?
মনে পড়ল, আন্দরকিল্লায় আমাদের বাসায় মাত্র একটা দৈনিক আর পাক্ষিক আনন্দমেলা রাখা হত। মাঝে মধ্যে বিচিত্রা আসতো। তবে, সেটা খুবই কম। আন্দরকিল্লা মোড়ে একজন হকার ছিলেন। ওনার নাম হাফেজ আহমদ। এইট বা নাইনে থাকতে একদিন উনি আমাকে ডেকে যা বললেন তা মর্মার্থ খুব সহজ। উনি আমাকে দেখেছেন যে, আমি নানান উছিলায় ওনার পত্রিকা স্ট্যান্ডের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করি দিনে কয়েকবার এবং ঘুরেফিরে বিচিত্রা, বিজ্ঞান সমাজ পত্রিকা ইত্যাদি উল্টেপাল্টে দেখি। কিন্তু কিনি না!
বুঝলাম আমার জারিজুরি শেষ! বললাম – আর করবো না।
উনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যা বললেন সেটা শোনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। উনি বললেন যে, উনি আমার পড়ার আগ্রহটা লক্ষ্য করেছেন। এবং খুশী হয়েছেন। ওনাকে ফাঁকি দিয়ে পড়ার দরকার নাই। আমি যেন যখন যেটা পড়ার ইচ্ছা সেটা এসে ওনাকে বলি। উনি তাহলে আমাকে পাশে দাড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। এরপর থেকে আন্দরকিল্লা মোড়ে দাড়িয়ে নানান সাপ্তাহিক আর দৈনিক পত্রিকা পড়ার সুযোগটা আমি কখনো হাতছাড়া করি নাই।
আউল্লাহর কমনরুমে একসঙ্গে এতো ম্যাগাজিন আর পত্রিকা দেখেতো আমার মাথা খারাপ হওয়ার দশা! কাজে প্রতিদিন ক্লাস শেষে আমার অবধারিত গন্তব্য ছিল কমন রুম। সেখানে ক্যারম খেলতে গিয়ে একজন দুইজনের সঙ্গে পরিচয় হতে শুরু করেছে। তবে, বেশিরভাগই সিনিয়র কারণ নতুনরা সবাই পড়ালেখা নিয়ে ব্যস্ত!
তো, বাবু ভাই আর আনিস ভাই-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার ১-২ দিনের মধ্যেই জাতীয় ছাত্রলীগের নবীনবরণ। আমি জানি আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ডাকা হবে। কিন্তু আমার কি সেখানে বক্তৃতা দেওয়া ঠিক হবে? আমি তো এর মধ্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ওখানে এই কাজ করে ফেলেছি।
তো, কী করি? গেলাম সিনিয়র কালাম ভাই, শাকিল ভাইদের ওখানে। ওনারা সব শুনে বললেন, পুরো নবীনবরণ অনুষ্ঠানটা তুমি এই বারান্দায় (তীতুমিরের ২০৮ নম্বর রুমের) বসে দেখ। তোমাকে ডাকলে তুমি যাবানা। কারণ একজন সবার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়া ঠিক না। কাজে জাতীয় ছাত্রলীগের মঞ্চ থেকে মুনিরের নাম ধরে ডাকাডাকি হলেও তাকে পাওয়া গেল না। আমি বরং গান শুনে রুমে ফেরৎ গেলাম। কাজটা ভাল হলো না খারাপ সেটা অবশ্য বুঝলাম না।
এর মধ্যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগ মিছিল হয়। আমি মিছিল গুলোতে যোগ দেই। তবে, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মিছিলে যাই না, জাতীয় ছাত্রলীগেরটাতেও না। এমনকী যখনই এনামুল ভাই চিৎকার করে বলতেন – প্রতিরোধে প্রতিশোধ কিংবা রক্তে নেব প্রতিশোধ তখন কিন্তু রক্ত চনবন করে উঠতো, কিন্তু দলীয় মিছিলে যেতাম না। অপেক্ষা করতাম কখন আলাদা আলাদা মিছিলগুলো নজরুল ইসলাম হলের কেন্টিনের সামনে জড় হবে এবং সেটি হয়ে যাবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিল। তখনই মিছিলে ঢুকে পড়তাম।
সুবীরদার কথা আগে বলেছি। ওনার সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথা হতো। তিনি কখনো আমাকে বলতেন না যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগে যোগ দাও। রাজনীতির আলাপই হতো কিন্তু কখনোই আমাকে প্রভাবিত করতেন না। এমনকি আমাদের হলে থাকেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াসেল কবীর (কবীর ভাই) মিছিলে যাবার সময় হাই-হ্যালো করেন, কিন্তু চলো এটা বলেন না। বলেন – মিছিলে যাবা নাকি, মুনির?
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে পরিচয় হল একজন লম্বা মত সিনিয়রের সঙ্গে। আহসানউল্লা হলে ঢুকে করিডর দুইদিকে গেছে। সোজা গেলে রুম শুরু হয় ১২৭ থেকে। সেখানেই আমি থাকি। আর ডানদিকদিয়ে সোজা গিয়ে একটু বামে গিয়ে মাঠ দিয়ে বের হয়ে কেন্টিনের পথ। ঐদিকে প্রথমে অতিথি কক্ষ এবং তারপর ১২০, ১১৯ হয়ে ১১১। তারপর হলের অফিস। খাওয়ার রুম ইত্যাদি। মেসে খাওয়ার ব্যাপারটাও শুরু হয়ে গেছে। সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। তবে সেটা এখন থাক।
বলছিলাম আমার মত আর একজন যিনি কিনা কোন দলের মিছিলে যান না কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে যান। ১১৯ নম্বর রুমে থাকেন। টুকটাক কথা বলার পর জানতে চাইলেন – হোয়াট ইজ টু বি ডান পড়েছ? কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো? সংশপ্তক?
খাইছে। কয় কি। এইগুলার নামই তো শুনি নাই। এই সব আবার কিসের বই। সংশপ্তক পড়ি নাই। কিন্তু বিটিভির কারণে কানকাটা রমযানের নাম মনে আছে।
আমার চেহারা দেখে বুঝলেন। বললেন – তোমাকে তো আমি সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে দেখি। ছাত্রলীগের নবীনবরণে নাকি এরশাদকে ব্যাকরনের পাঠ দিয়েছো আর এই সব কিছুই পড় নাই!
তো, মাহমুদুজ্জামান রুমি ভাই আমাকে প্রথম বললেন, তুমি সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে আসো এটা ভাল। কিন্তু তুমি যদি সত্যিকারের পরিবর্তন চাও তাহলে তোমাকে কোন না কোন দলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। নাহলে তুমি এই প্রসেসের সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে না।
-তিনিও কেন একই কাজ করেন না। এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন তার দলের কোন শাখা বুয়েটে নাই দেখে তিনি সরাসরি সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে যোগদেন।
পরের কয়েকদিন আমি খুব ভাবলাম। তারপর বুঝলাম যে, ওনার কথাই ঠিক। আমাকে অবশ্যই কোন না কোন দলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এর মধ্যে গোলাম মোস্তফা নামে কেমিকেলের একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। স্কুল ম্যাগাজিনে লেখা ছাপা হয়েছে বলে নিজেকে একটু-আধটু লেখক ভাবে। তো মোস্তফার গল্প দেখলাম ইত্তেফাকে ছাপা হয়েছে। সেটার কাটিং সে হলে নিয়ে এসেছে। নিজের লেখালেখির কথা চেপে গেলাম। মোস্তফার সঙ্গে আলাপের অনেকখানি জুড়ে থাকতো জাতীয়তাবাদের কনসেপ্ট নিয়ে। আমরা বাঙ্গালি না বাংলাদেশি। বুয়েটে ছাত্রদলের তেমন একটিভিটি নাই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পলাশী যুদ্ধের সময় তৎকালিন ঢাকার মেয়র আবুল হাসনাত বুয়েট ছাত্রদের বিরোধিতা করেছিলেন। সেই কারণে ছাত্রদলের তেমন একটা বেইল নাই। পলাশী যুদ্ধের সময় যারা ফার্স্ট ইয়ারে ছিল তারা মাত্র গতবছরে ক্যাম্পাস ছেড়েছে। তারমানে এখন যারা দ্বিতীয় বর্ষে তাদের মধ্যে পলাশী যুদ্ধের অভিজ্ঞতালাভকারীরা কেও নাই।পলাশী যুদ্ধের ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ছিল আশির দশকের বুয়েটে। তবে সেটা মনে হয় আমার নোটের সঙ্গে যায় না!
যাইহোক আমি আমার রাজনীতির ভবিষ্যৎ ভাবি। আমার পথ কী হবে? বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র? প্রতিরোধে প্রতিশোধ? রক্সে নেব প্রতিশোধ? প্রকৌশলী সিরাজ শিকদারের দেখানো পথ? নাকি বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ? না কি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ?
বঙ্গবন্ধুর আদর্শেই যদি থাকি তাহলে কোথায় থাকবো? জাতীয় ছাত্রলীগ না কি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ?
প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তর ওতো জানা!
৬.
পড়তে আসছি ইঞ্জিনিয়ারিং। কিন্তু ওমা এখানে দেখি বলে তড়িৎ কৌশল। আর পড়তে দিসে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অংক, ইংলিশ, অর্থণীতি এরকম সব হাবিজাবি বিষয়। সারাদিনই এসবের ক্লাস। ফাকে একটা বেসিক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর বেসিক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। মনে খুবই কস্ট নিয়ে ক্লাসে যাই। সেসময় বিটিভিতে খালি বিজ্ঞাপন দেখাতো। বলা হতো বিজ্ঞাপনই সেখানে আসল। বাকী সব ফিলার। আর আমি এসে দেখলাম ফিজিক্স/কেমিস্ট্রি ম্যাথের ফাকে সামান্য করে ইঞ্জিনিয়ারিং করানো হচ্ছে!!!
আমি পড়ে এসেছি চট্টগ্রাম কলেজে। ওখানে প্রত্যেক পিরিয়ডে আমাদের এক বিল্ডিং থেকে অন্য বিল্ডিং-এ যেতে হত। আর এখানে, একটা ড্যাম খাওয়া বিল্ডিং-এর মধ্যে ২১৬ নম্বর রুমেই সব করে ফেলছি। ওখানে বেশিরভাগ সময় যারা ক্লাস নিতে আসেন তাঁরা কেও ইঞ্জিনিয়ার নন। অংক করতে হবে, অর্থনীতি মুখস্ত করতে হবে, কেমন করে চিঠি বা টেন্ডার নোটিশ লিখতে হয় সেগুলো শেখার জন্য বুয়েটে আসছি!!!বাসায় গিয়ে কী বলবো। এক আরপি ওয়ার্ড দিয়ে কতটুকু কী করা যাবে।
আবার একটাই ল্যাব যেটার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে সেটার নাম মডেল ল্যাব। মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে সেই ল্যাবে প্রথমদিন গিয়ে মনে হল যাক অন্তত এই ল্যাবের কথা গ্রামে গিয়ে বলা যাবে। হা হতোম্ভি। প্রথমদিনেই বলা হল এটা মডেল ল্যাব, রিয়েল ল্যাব না। মানে ওখানে নানান ধরণের মডেল আছে। আর ক্লাসটাও সহজ। গ্রুপ স্টাডি করে একটা রিপোর্ট লিখতে হবে আর ভাইভা দিতে হবে। রিপোর্ট শুনু বুঝলাম একটা টপশীট লাগবে। পরক্ষনে বুঝলাম না এটাতে টপশি লাগবে না কারণ সবগুলো রিপোর্ট একটা খাতাতে হবে। তবে, এখানে রিপোর্ট লিখতে হবে ল্যাবে বসে। আড়াইঘন্টা সময়, বই পত্র ঘেটে, রিপোর্ট লিখতে হবে। এইটুকু ঠিক ছিল। কিন্তু যখন বলা হল একেক গ্রুপ একেক ল্যাব করবে তখন একেবারে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। কারণ ক্লাসে মাত্র বয়লার পড়ানো শুরু হয়েছে আর আমার গ্রুপের ভাগে পড়েছে টারবাইন!!!
টারবাইনের টওতো রশীদ স্যার ক্লাসে পড়াবেন না এখন তাহলে কেমনে পারবো? হলে ফিরে যখন অন্যদের কাছে সবক নিতে গেলাম তখন বলা হল – আরে তোমাদের তো আসল কথায় স্যাররা বলেন নি।সেটা কী?-রিপিট। মানে হল মডেল ল্যাবে স্যাররা মোটামুটি যেটা দ্যান সেটার নাম হল বাঁশ। কঠিন বাঁশ। যাহোক সব শুনেটুনে বুঝলাম এটা আর আমার পাস করা হবে না। যতদিন মডেল ল্যাব করেছি প্রতিদিনই ব্যাপক টেনশনে থাকতাম। কারণ এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করা হতো যে একটা উত্তর দিতামই। যে কয়জন স্যার ছিলেন তার মধ্যে ম তামিম স্যার ছিলেন (২০০৭-৮ সালের প্রধান উপদেস্টার বিশেষ সহকারি) অসাধারণ। ওনার চেহারা দেখে কখনোই বোজা যেত না আমার উত্তরটা হয়েছে কী না। যেমন একবার আমাদের জাহাঙ্গীর (ড. জাহাঙ্গীর এখন ফিনল্যান্ডে মনে হয়) যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফেরৎ আসলো। বললো- আজকে স্যার খুশী হয়ে ওর পিঠ ছাপড়ে দিয়েছে। কাজে আজকে ও ১০-এ ৯। (স্যার কাউকে ১০-এ ১০ দিয়েছেন এমনটা আমি মনে করতে পারছি না)। আমি জাহাঙ্গীরের কাছে জানতে চাইলাম প্রশ্নটা কী ছিল দোস্ত।- সোজা। স্যার জানতে চাইছে – পেট্রোল ইঞ্জিনে একটা কার্বুরেটর থাকে। ডিজেল ইঞ্জিনে কয়টা থাকে?-তুই কী বললি। -কেন। যেটা সত্য। দুইটা।- আমি আর সাকিব মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। স্যার কেন পিঠ চাপড়েছে সেটা আমি অনুমান করতে পারলেও বলতে পারলাম। দিন শেষে স্যার যঅন নস্বর বললেন তখন দেখা গেল জাহাঙ্গীরকে রিপিট (মানে আবার ঐ ল্যাব করতে হবে) দিয়ে রাখছে।মডেল ল্যাবে যাবার সময় আমরা সব জানা দোয়া পড়ে ফেলতাম যাতে তামিম স্যারের হাতে না পড়ি। বেশরিভাগ দিনই দোয়া কাজে লাগতো না। (তামিম স্যার সম্পর্কে আমার ভয় কিছুটা কাটে সেকেন্ড ইয়ারে, আর পুরাপুরি কেটে যায় যখন তিনি কম্পিউটার সেন্টারে কিছুদিন সিস্টেমস এনালিস্ট ছিলেন তখন। ২০০৭-৮ সালে স্যার যখন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারি তখন আমি সেখানেই চাকরি করি। সেই অভিজ্ঞতা আলাদা।)
কেমিস্ট্রি ক্লাসে একজন শাদা-চুলের আইনস্টাইন ক্লাস নিতে আসলেন। দেখতে একেবারে আইনস্টাইনের মত। হাতের লেখা ছোট। ক্লাসে এসেই প্রথমে ব্ল্যাকবোর্ডের কোনায় লিখতেন PV=nRT । এটি আদর্শ গ্যাসের সূত্র। তারপর বলতেন প্রকৃতিতে কোন আদর্শ গ্যাস নাই। ফলে ঐ সূত্রে ঝামেলা আছে। ঔ ঝামেলাটা সলভ করাটাই হল স্যারের ক্লাসের উদ্দেশ্য। বেশিরভাগ কথাই বুঝতাম না। কিন্তু সব কিছু লিখে নিয়ে আসতাম। এই সময় আমাদের ক্লাসের একজন শুকনা পাতলা ছাত্রের সঙ্গে আমার একটু খাতির হল- আযম খান। রাজশাহী বোর্ড থেকে ডাবল স্ট্যান্ড করে এসেছে। তো, সে দেখতাম তেমন একটা কিছু ক্লাসে লিখি টিখে না। ব্যাপারকী?
-দূর মুনির। লিখে কোন লাভ নাই। পরীক্ষার আগে “চোথা” যোগাড় করলেই হবে।
-“চোথা আবার কী?”
-চিনে যাবে। চিনে যাবে চিন্তা নাই।
আমার অবশ্য ততদিনে অন্য চিন্তা শুরু হয়েছে। আমি বুঝে ফেলেছি বুয়েটর পড়ালেখা খুব কঠিন। এখানে পাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রতিদিন বিকালেই শুধু যে ল্যাবের অত্যাচার তা না। ক্লাসটেস্ট নামে একটা পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। পরীক্ষা হচ্ছে ক্লাসের মধ্যে। শুনে তেমন একটা ভয় পাই নাই। কারণ ৬০ জন। পাশের জনের হেল্প তো পাওয়া যাবে। তো সার্কিট পরীক্ষা দিতে গিয়ে সে গুড়ে বালি। কারণ দুইটা রেসিস্ট্যান্সের ভ্যালু হচ্ছে “তোমার রোল নম্বর”। বোঝ ট্যালা। এর মধ্যে একদিন শুনলাম একটা খুশীর খবর। মিড-সেমিস্টার ব্রেক নামে দুই সপ্তাহের ছুটি হবে মার্চের ২২-২৩ তারিখে। রুমি ভাই-এর সঙ্গে আলাপ হয় যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটা আমার কর্ম না। আমি চলে যাবো দেশে। আমি দিন গুনতে থাকি। ভাবি কয়েকদিনের মধ্যেই আমার মুক্তি। ২২ তারিখ রাতে রূপালী এক্সপ্রেসের একটা টিকেট কেটে আনি। আমার ব্যাগ গুছাই। একবার ভাবলাম মশারী, তোষক নিয়ে বের হয়। পরে ভাবলাম এগুলো নিয়ে যেতে গেলে সবার চোখে পড়বে। ব্যাগ গুছানোর পর দেখলাম কিঞ্চিৎ জায়গা আছে। ওয়ার্ড সাহেবের আর কয়েকটি বই নিলাম। সবাইকে বলতে পারবো আমি ৬ সপ্তাহ বুয়েটে পড়েছি। বিশ্বাস না করলে সে বইগুলো দেখাতে পারবো। যেদিন ছুটি হল সেদিন আমি খুবই উত্তেজিত। কারণ আজকেই বুয়েটে আমার শেষদিন। আমি যে একেবারে চলে যাচ্ছি বাড়িতে এটা কেবল রুমী ভাই জানেন। তিনি বললেন – ঠিক আছে যাও। আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাইখো। আমিতো এই বছর আছি, কাজে হলের ঠিকানায় চিঠি লিখলে আমি পাবো।রুমী ভাই আমাকে হলের গেট পার করে রিকসায় তুলে দিলেন। আমি ফুলবাড়িয়ায় এসে রুপালীর বাসে উঠে পড়লাম। রাত ১১টার দিকে বাস ছাড়লো। আমি একটু পেছন ফিরে তাকালাম।আমার চোখ দিয়ে কি কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছে? চোখের কোন কি ভিজে উঠেছে?বলতে পারবো না।
ততক্ষণে গাড়ি রওনা হয়ে গেছে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে বুয়েটকে বিদায় জানালাম। মনে কোন কষ্ট নাই অবশ্য। কারণ আমি তো বুয়েটে পড়ার মত না। কাজে আগে চাটগাঁয় যাই।
বিদায় বুয়েট।
৭.
বাস চলতে শুরু করল। এখনকার মতো আরামের গাড়ি নয়। দূরপাল্লার হিনো গাড়ি। প্রথম ফেরি মেঘনা ঘাটে আর এর পরেরটা দাউদকান্দিতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমানোর উপায় নাই। গাড়িতে কোন টেলিভিশন নাই তবে একটা ক্যাসেটে নানান পদের গান চলতে থাকে। ফুলবাড়িয়া থেকে বের হয়ে গাড়ি যাত্রবাড়ি পার হয়ে ডেমরা রোডে উঠো পড়ার পর পর ঢাকা শহরের আলোর রেখা মিলাতে থাকে। আমার মনে ভেসে ওঠে নানান মুখ। সবচেয়ে বড় হয়ে প্রথমে হাজির হোন বাদল ভাই।
আমি এইচএসসি পাশ করি ১৯৮৪ সালে। তারও আগে, আমাদের পাড়ায় একজন সিনিয়র ভাই ছিলেন, শহিদুল ইসলাম বাদল (প্রকৌশলী, বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী)। বাদল ভাই ছিলেন আমাদের বন্ধু, ফিলসফার এবং গাইড। স্কুলে অঙ্ক নিয়ে কোন ঝামেলা হলে তার কাছে যেতাম, ইন্টারে ম্যাথের প্রাইভেটটাও তাঁর কাছে পড়েছি। তো, বাদল ভাই-এর কাছে জীবনের লক্ষ্য ছিল একটা- বুয়েটে ভর্তি হওয়া। কিন্তু তিন হাজারের গ্যাড়াকলে তিনি বুয়েটে পরীক্ষা দিতে পারেননি, পড়েছেন চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। তিন হাজারের গ্যাড়াকল মানে হল ইন্টারে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর ম্যাথে ৬০ এর ওপরে পেলেই বুয়েটে দরখাস্ত করা যেত। তবে দরখাস্ত করতে পারলেই সেখানে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া যেত না। বুয়েট কর্তৃপক্ষ যত এপ্লিকেশন পড়তো তাদের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর ম্যাথের মার্ক যোগ করে নতুন একটা মেরিট লিস্ট করতো। এই লিস্টের প্রথম থেকে ৩০০০ তম পর্যন্ত সবাইকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে দিত। তবে, বুয়েট কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠুর ছিল না। তারা ৩০০০তম শিক্ষর্থীর যে নম্বর হতো, সেই নম্বর আরো যাদের থাকতো সবাইকে পরীক্ষা দিতে দিত। ফলে মোটেমাটে ৩১০০ বা সেরকম ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিতে পারতো। ১৯৮১ বা ১৯৮০ সালে সেরকম ৩০৬৮ তম ব্যক্তিটি কিন্তু বুয়েটে চান্স পায়। (এই সিস্যাটেমটা আমাকে অনেক ভাবাতো। আলী মুর্ত্তাজা স্যার ভিসি হওয়ার পর এই খেলাটা শেষ হয়। আমি খুশী যে, এই খেলা শেষ করার অংকটা আমি করতে পেরেছিলাম)
যাইহোক, বাদল ভাই দুইবার আবেদন করেও পরীক্ষা আর দিতে পারেননি। ভর্তি হয়েছেন চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। আমরা যারা তার ছোট তাদেরকে দেখা হলেই তিনি একটি মন্ত্র দিতেন – ফার্স্ট ডিভিশন বা স্টার কিংবা স্ট্যান্ড করাটা কোন কাজের কাজ না, যদি তুমি বুয়েটে ভর্তি হতে না পারো!!! আর বুয়েটে ভর্তি হওয়ার জন্য কেবল দরকার ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর ম্যাথ! তিনি আবার অন্য গল্পও করতেন। যেমন রেজাউল করিম স্যার যখন তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ তখন তিনি ভর্তি পরীক্ষার একটি সভা ডাকেন। সেখানে এক স্যারের হাতে একটা ভর্তি গাইড ছিল। সেটার নাম বিদ্যুৎ। তো, স্যার জানতে চাইলেন সেটা কি?
-এখানে পুরানো ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আছে। ছেলে-মেয়েরা এটা পড়ে প্রিপারেশন নেয়।
-কী!!! বিদ্যুৎ পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হবে। ঠিক আছে। এই বছর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আমি করবো। সেই সময় কলেজগুলোতে ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা হত। শোনা যায়, ভর্তি পরীক্ষাতে ৭২ নম্বর গ্রেস দিয়ে সেবার ছাত্র ভর্তি করাতে হয়েছে!!!
আর বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা যে, পৃথিবী গ্রহের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা সেটা বাদলভাই আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন। প্রথমত এখানে কোন সাজেশন নাই। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর অংক প্রতিটা থেকে ২০টি করে মোট ৬০টি প্রশ্ন। ১০ নম্বর করে ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা।
সময়?
-তিন ঘন্টাই! বাদল ভাই-এর পাল্লায় পড়ে আমার এমন অবস্থা হল যে, আমি বাংলা আর ইংরেজি পড়া বাদই দিলাম। খালি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর ম্যাথ। এমনকি সাজেশনের তোয়াক্কা না করে বইগুলোর সব কাল কাল অংশ পড়ে ফেলেছি। প্ল্যান করে, প্রতি সপ্তাহে কী পড়বো, এইসএসসির কাঁথা পুড়ে খালি বুয়েটের জন্য পড়া। চট্টগ্রাম কলেজে আমাদের বারে অনেকেই স্ট্যান্ড করেছে। তবে, আমি দাড়াতে পারি নাই। আমি যেদিন মার্কশীট আনতে যাই, তখন মোজাম্মেল স্যার আমাকে বলেন – তুই চেষ্টা করলে একটি বিশ্বরেকর্ড করতে পারতি।
– কোনটা স্যার।
– ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ম্যাথে লেটার মার্কসহ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ফেল করা!
স্যার এই কথা বলছিলেন আমার বাংলা আর ইংরেজির দুরবস্থা দেখে। সেগুলোতে আমি কোনমতে পাস করেছি (নম্বর কত এটা না হয় না বলি। পোলাপান আমার নোট পড়ে)। আর জয়নাব ম্যাডাম তো মারতে উঠলেন কারণ আমি নাকি কলেজে জীববিজ্ঞান অংশে যত বেশি নম্বার পাওয়া সম্ভব সব পেয়েছি কিন্তু উদ্ভিদ বিদ্যা খাতায় কিছু লিখি নাই।
-ম্যাডাম, বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় বায়োলজি নাই। এটা বলেই আমি দৌড় দিয়েছিলাম।
এদিকে বাদল ভাই-এর অত্যাচারে ইন্টার পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র সাতদিন পরই টেবিলে পড়তে বসি। দাদী ক্ষেপে গিয়ে বললো – তোর না পরীক্ষা শেষ। বেড়াতে যা। আমাকে বাঁচাতেন আমার দাদা বলতেন ওরে পড়তে দাও।এর মধ্যে একদিন শুনলাম বুয়েটে ভর্তি হতে হলে কোচিং করতে হয় ঢাকাতে। কাজে আমাকেও করতে হবে। বাকীরা কি করবে?
আমি, আলী, শাহেদ, তানভীর, অলক এবং আরো কয়েকজন মিলে ঠিক করলাম আমাদেরকেও কোচিং করতে হবে। সব খোঁজ খবর নিয়ে ঠিক হল আমরা সবাই কোচিং-এর টাকা নিয়ে ঢাকায় চলে যাবো। তিনভাগ হয়ে একভাগ আমার চাচার বাসায়, একভাগ তানভীরের খাচ্চু (খালু+চাচ্চু)র বাসায় আর একভাগ অলকের কাকা (বা ফুফু)র বাসায় থাকবো। সেই হিসাবে আমরা ঢাকায় আসলাম। প্রত্যেকে চাচা-খালার কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছি। আসার পরদিন আমরা একজায়গায় জড়ো হলাম। এর মধ্যে দুইটা কোচিং সেন্টারের খোঁজ নিয়ে বোঝা গেল ওখানে পড়া যা, না পড়াও তা। কাজে আমরা ঠিক করলাম প্রতিদিন সকালে আমরা নিজ নিজ ডেরা থেকে বের হব। তারপর সবাই এসে স্টেডিয়ামের সামনে, গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনে জড়ো হব। তাই সই। আমরা প্রতিদিন সেখানে জড়ো হই। তারপর দলবেধে বেড়াতে বের হয়ে যাই। একদিন সংসদ ভবন, একদিন সোনারগাঁও, একদিন স্মৃতিসৌধ এভাবেই আমাদের কোচিং চলতে থাকে। এর মধ্যে আমরা ফরম জমা দিতে যাই বুয়েটে। তানভীরের ফরমের এটাসটেশন ছিল না। সেটার জন্য আমরা সবাই মিলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে আমার চাচার কাছে যাই। চাচা তার কলিগদের ডেকে পরিচয় করিয়ে দেন। বিশেষ করে তানভীর তাহেরকে। ও ইন্টারে মাত্র ৯৫৬ পেয়ে কুমিল্লা বোর্ডে ফার্স্ট হয়েছে। তো এভাবেই আমাদের কোচিং আগাতে থাকে। চাচীরা বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে কারণ কোচিং-এ আমরা প্রতিদিন টায়ার্ড হয়ে ফিরতাম। তাই রাতে সবাই টেলিভিশন দেখতাম! যাইহোক, কিছুদিনের মধ্যে আমাদের টাকা ফুরিয়ে গেল। আমরা তখন জানালাম আমাদের কোচিং শেষ। আমরা চিটাগাং চলে যাই। ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসবো। মনে পড়লো বাবার কথা। বাবার একটা গোপন ইচ্ছা ছিল আমাকে ডাক্তারী পড়ানোর। কাজে যেদিন বুয়েটে ফরম জমা দেওয়ার টাকা নিয়েছি সেদিন বলেন – ডাক্তারী পরীক্ষা যেহেতু একটা, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ও কেবল একটা দিতে পারবা। ডাক্তারী পড়বো না বলে মেডিকেল ভাইভাতে অনেক ক্যাচাল করলাম। বোর্ডরে অনেক ক্ষেপাই দিলাম এবং ঐদিনের সবচেয়ে কম নম্বর পেলাম।
যথারীতি বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছি। প্রথমদিন ইঞ্জিনিয়ারি আর পরের দিন স্থাপত্য। আবার তিন চাচার বাসায়। আমার সিট পড়েছে বুয়েটের লাইব্রেরিতে। আমার দুইপাশে যথাক্রমে যশোর আর ঢাকা বোর্ডের দুইজন। দুইজনই আমার কাছে জানতে চাইল – আমার প্লেস কত? হলে আমিই ছিলাম একমাত্র যে বোর্ডে প্লেস করে নাই কিন্তু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথে প্রায় ৯০% নম্বরের কাছে পেয়েছে! বাদল ভাই-এর কথা মনে রেখে আল্লাহর নামে শুরু করলাম। কিছুক্ষনের মধ্যে বুঝলাম আমারে দিয়ে হবে না। খাতা দিয়ে বের হয়ে যেতে চাইলাম। যিনি গার্ড দিচ্ছিলেন (পরে জেনেছি মশিউর রেজা স্যার, চট্টগ্রামের) তিনি আমাকে বললেন – টাকা দিছ না। কস্ট করছো না। তিন ঘন্টা বসে থাকলে কী হবে। বন্ধুরা কি বের হবে?
– বললাম। স্যার। অংকগুলো কিছুই তো পারি না।
-বললেন। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি করো।
কী আর করা। যা মনে আসে করেটরে সময় কাটালাম। কিছু কিছু অংকের, ফিজিক্সের রেজাল্ট দেখে বুঝলাম সেগুলো হওয়ার কোন কারণ নাই। পরীক্ষা শেষে হল থেকে বের হলাম পাংশু মুখে।বাকীদের সঙ্গে উত্তর মেলানোর চেস্টা করলাম এবং তৎক্ষনাৎ বুঝলাম যা করার করে ফেলেছি। আমাকে মেডিকেলই পড়তে হবে!
পরেরদিন আমরা ঘুরে বেড়ালাম। শাহেদ আর তানভীর পরীক্ষা দিল মনে হয়। রাতে চট্টগ্রাম চলে গেলাম। বাসায় কিছু বলি না। মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াই। মা জানতে চাইলেন। বললাম – চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফরম তুলবো। যেহেতু বাবার সঙ্গে ওয়ান মেডিকেল –ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চুক্তি কাজে ফরম কেনার টাকা নাই। মা বললেন – তোর দাদীরে দিয়ে বলা। মায়ের কথাতো তোর বাপ ফেলবে না। আমিও তাই দাদীরে বললাম বাবাকে পরেরদিন অফিস যাবার সময় যেন আমাকে ১৫০ টাকা দিতে বলে। ব্যাস কাজ খতম।এর মধ্যে মেডিকেলের রেজাল্ট দিয়ে দিয়েছে। সিএমসি হয়ে গেছে। তবে, ভর্তির জন্য মাসখানেক সময় আছে। এর ভেতরে বুয়েটের রেজল্ট দেওয়ার কথা। আর রাঙ্গুনিয়ার পরীক্ষা। আন্দরকিল্লায় আমাদের বাসার পেছনে একটা মাঠছিল। সেখানে রাতে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলি। আমাদের দোতলার বাসা থেকে মা সরাসরি জানালা দিয়ে আমাদের ডাকতে পারেন। তো সেদিন রাতের দিকে জানলা খুলে মা ডাকাডাকি শুরু করলেন।
– কী ব্যাপার। ডাকো ক্যান।
– তোর বাবলা ভাই (প্রকৌশলী, সে সময় পরমাণু শক্তি কমিশনে চাকরি করেন আর বুয়েটে মাস্টার্স করেন। একটা লুনা মোটর সাইকেল আছে। বেইলি রোডে খালার বাসায় থাকেন) ফোন করে বলছে – বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট দিছে কতক্ষণ আগে। চান্স পাইছো।
তারপর মা আমার রেজাল্টে যে পজিশন বললেন তাতে আমার পুরাই টাসকি অবস্থা।-
মা, বাললা ভাই (বাবলা ভাইকে আমি ছোট বেলাতে বাললা ভাই বলতাম, এখনো বলি) তো আমার রোল নম্বরই জানে না। কেমনে রেজাল্ট দেখছে।
– তোর নাম বলছে তো।
– আরে না। তুমি ভাইয়াকে আমার রোল নম্বর দাও। আর আমার মনে হয় আমার যে পজিশন বলছে সেটা ওয়েটিং লিস্টের হবে। মেরিট লিস্টের না।
তারপর সেটা ভুলে খেলে টেলে রাতে বাসায় এসে শুনলাম এই শীতের মধ্যে বাবলা ভাই আবার বুয়েটে গিয়ে রেজাল্ট দেখে এসেছে এবং আগেরটাই সঠিক। মানে আমি যা ফার্স্ট চয়েজ দিয়েছি সেটাই পাবো। তার আগে ভর্তি পরীক্ষার ফরম নিতে যখন আসি তখন শুনলাম সবার পছন্দ হলো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। মানে সেটা হল ফার্স্ট চয়েজ। যেমন মেডিকেল ডিএমসি। কাজে, সবার মত আমিও সেটাই দিয়েছি। কিন্তু তখন জানতাম না ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপারটা কী? সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সঙ্গে ইলেকট্রিক্যালের পার্থক্য কে জানে? আমি তো জানি না। আমার চাচা, তখন রেলের বড় প্রকৌশলী, নিজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বললেন ইলেকট্রিক্যালএর তো চাকরি নাই, পড়ে কী হবে! তারপরও অন্যদের থেকে তো পিছায় থাকতে পারি না।
তো, আমার বাবার ১৫০ টাকা জলে গেল। আমার আর চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পরীক্ষা দিতে হবে না।
আমি ব্যাগ-ট্যাগ গুছায়ে ঢাকা চলে আসলাম। স্বাস্থ্য পরীক্ষা হচ্ছে। এক ডাক্তার চোখের কী জানি দেখলেন।
তারপর ফরমে কী জানি লিখে দিলেন। লেখাটা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে ফরমের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।
টেম্পারারিলি আন ফিট ফর ইঞ্জিনিয়ারিং!!!!!
৮.
বাসটা হঠাৎ ঝাকি খেয়ে থেমে গেল। বুঝলাম মেঘনা ঘাটে এসে পড়েছি। আমার ফ্ল্যাশব্যাকও থেমে গেল। ফেরীতে বাস পার হওয়ার সময় ফেরিঘাটে বা ফেরিতে ডিমভাজি-পরোটা খাওয়াট বেশ ভাল। কিন্তু আজ আর আমার মন ভাল নেই। নানান সব কথা মনে পড়ছে। বুয়েট থেকে আমার অগত্যা যাত্রা কী না!
সেদিন অন্যদের শেষ না হওয়া পর্যন্ত বুয়েট মেডিকেলের সামনে বসে থাকলাম। তারপর ঐ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলাম। উনি আবার দেখলেন। বললেন – কবে থেকে চশমা?-ক্লাস এইট। -হুম। আচ্ছা। আমার মনে হচ্ছে পারতে পারো। তবে, আমি তো আর এখন কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারবো না। তুমি বরং চীফ মেডিকেল অফিসারের সঙ্গে দেখা কর।গেলাম। আমার তখন কাপুনি নিয়ে জ্বর আসার অবস্থা। আম-ছালা-ছালা বাঁধার রশি সবই তো শেষ। তিনি সব দেখে শুনে বললেন – কোন একজন চক্ষু প্রফেসরের সঙ্গে দেখা কর। তিনি যদি রাজী হোন তাহলে আমি তোমাকে আর একবার দেখবো। ফরম নিয়ে সেখানে খসখস করে লিখে দিলেন – Report after 7 days with an specialist recommendations।
বুঝলাম কোন লাভ নাই। ঢাকা শহরে চোখের প্রফেসর বলতে প্রফেসর আহমদ শরীফ বা প্রফেসর হারুন। তাদের কারো এপয়েন্টমেন্ট এক মাসের আগে পাওয়া যায় না। চাচার বাড়িতে গেলাম। (এবার আমি একা কারণ আমার সঙ্গে আগে যারা ছিল তারা সবাই মেডিকেলে পড়বে)। চাচা অফিস থেকে ফিরলেন। চাচী গবেষণা করে বের করলেন তার বোন (মানু খালা, শহীদ আনোয়ার স্কুলের শিক্ষক) এবং প্রফেসর আহমদ শরীফের স্ত্রী বাল্যবন্ধু। মানু খালাম্মার বাসায় গেলাম। তিনি একটা দিন বললেন। তার সঙ্গে বকশিবাজারে প্রফেসর আহমদ শরীফের বাসভবন + চেম্বারে। ওনার স্ত্রী, মানু খালাম্মার বান্ধবী জানালেন ওনার একটা বিশেষ ব্যবস্থা আছে। উনি আমাকে নিচে পাঠিয়ে দিলেন।
ঢাকার কোন বড় ডাক্তারের চেম্বারে ঢোকা আমার এবারই প্রথম। একজন ইতিহাস লিখলেন। মানে আমার কী সমস্যা, কবে থেকে চশমা। বারেক নামে একজন চোখের প্রেশার দেখলো। (আমি ভেবেছিলাম বারেক মনে হয় কম্পাউন্ডার, পরে যা জেনেঝি সেটা না লেখাই ভাল) আর একজন ভিশন টেস্ট করলো। সবশেষে আমি সৌম্য, শান্ত একজন বয়সী ডাক্তারের সামনে বসলাম। ডাক্তারকে দেখে আমার মন ভাল হয়ে গেল।
– বুয়েট না মেডিকেল?
বুজলাম এতে উনি অভ্যস্থ। বললাম। উনি আমাকে দেখে বললেন – চোখে কেমন চাপ পড়বে।
আমি বললাম ইলেকট্রিক্যাল তো মনে হয় চোখের তেমন কারবার লাগবে না। খালি ভোল্টেজের সমস্যা!
উনি হেসে দিলেন। তারপর পাওয়ার এডজাস্ট করলেন। এবং বললেন – ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়লে অসুবিধা হবে।
-জি। অন্য কোথাও ভর্তি হতে পারবো না।
-আচ্ছা। তাহলে পড়। আমি লিখে দিচ্ছি। চোখে বেশি প্রেশার দেওয়ার দরকার নাই।
যাইহোক, ডা. আহমদ শরীফের রিকমেন্ডেশন দিয়ে আমি বুয়েটে ভর্তি হয়ে গেলাম। আর বাড়ি ফিরে গেলাম ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি।
জানুয়ারি ১৯৮৫ থেকে চট্টগ্রামে বাড়িতে বসে থাকা। ক্লাস শুরুর কোন খবর নাই। আড্ডা দিয়ে বেড়াব তার সুযোগও নাই। কারণ আলী, শাহেদদের মেডিকেলের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আমার চোখের সামনে দিয়ে ওরা এপ্রোন পড়ে, ভাব নিয়ে যায়। বাদল ভাই-এর সঙ্গেও আড্ডা নাই কারণ উনি ওনার ক্যাম্পাসে। তো, কয়েকজন পরামর্শ দিল কিছু বইপত্র যোগাড় করে পড়ালেখা করতে। সেজন্য মাঝখানে একবার খবর পেলাম কালাম ভাই বুয়েট থেকে এসেছেন। তার কাছে গেলাম। -তুমি ইচ্ছে করলে ক্যালকুলাসটা করতে পারো। তবে, যাই করো না কেন বুয়েটে গিয়ে কিন্তু সেগুলো আবারই পড়তে হবে। আমি দুইটা বই কিনলামও। দুই একদিন চেস্টাও করলাম। পরে ভাবলাম। ধুর। ছুটিটা ছুটিই থাক। অন্য কিছু বরং করা যাক। কী করা যায়? বুয়েট থেকে কোন আইডি কার্ড দেয় নাই। কাজে এখন কোন পরিচয় নাই।
একদিন দুপুরে কী মনে করে হাটতে হাটতে লালদিঘীর পাড়ে গেলাম। সেখানে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি। বললাম- আমি বুয়েটে ভর্তি হয়েছি কিন্তু কোন আইডি কার্ড নাই। তবে, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাসের কাগজপত্র আর বুয়েটে ভর্তি ফী দেওয়ার রশিদ আছে। আমি কি মেম্বার হতে পারবো? যার কাছে এই কথাগুলো বলেছি তিনি জীবনে মনে হয় এমন আবদার কখনো শুনেন নাই। অনেকক্ষন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ভিতরে গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলে এসে আমাকে একটা ফরম দিলেন। আর বললেন পরের দিন যেন পূরণ করে নিয়ে যাই। আমি তো মহাখুশী। পরেরদিনই ব্রিটিশ কাউন্সিলের মেম্বার হয়ে গেলাম। শুরু হল আমার টাইম পাসের বুদ্ধি। মেম্বার হওয়ার পর আবিস্কার করলাম ওখানে সব ইংরেজি বই!!!!হায় হায় ইংরেজি পড়ে সেটা বোঝার ক্ষমতাতো আল্লাহ আমারে দেয় নাই। পরে ভাবলাম, না বুঝি, হাতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটা বই থাকলে সবসময় লোকে আমার জ্ঞান নিয়ে কোন প্রশ্ন করতে পারবে না।প্রথম যে বইটা দেখে পছন্দ হলো সেটা একটা মোটা বই, আবার বেশি মোটা নয়। নাম- মার্ডার ইন দি ক্লাউড। লেখক আগাথা ক্রিস্টি! এই বইটা পছন্দ করার কারণ হল আগাথা ক্রিস্টির নাম শুনেছি। হারকিউল পয়েরো নামের গোয়েন্দা চরিত্রের স্রস্টা। তো, বানান করে, ডিকশনারী নিয়ে পড়া শুরু করলাম। পড়তে পড়তে মনে হল আরে এই গল্পতো আমি জানি। কোথায় জানি পড়েছি। পড়তে পড়তে এক সময় মনে হল। ব্যাস, চলে গেলাম রাইফেল ক্লাবের সামনে, বই ভাড়ার দোকানে। এই দোকান থেকে কুয়াশা আর মাসুদ রানা ভাড়া করে নিয়ে আসতাম। আমাকে দেখে দোকানদার বলল- আরে এতদিন কই ছিলেন।
-গম্ভীর গলায় বললাম –আমি এখন বুয়েটে পড়ি!
যাইহোক, মাত্র কয়েকবারে চেস্টায় কুয়াশা সিরিজের বইটা বের করে ফেললাম। তারপর এ দুই বই ভাড়া নিয়ে আসলাম। পরের কয়দিন মিলিয়ে মিলিয়ে পড়ে ব্যাপক আনন্দ পেলাম। বুঝলাম, কুয়াশা সিরিজের ঐ দুই পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায় মূল বই পড়ে সেই আনন্দ পাওয়া যায়। পরের কয়েকদিন তাই খালি কাজি আনোয়ার হোসেনকে সালাম দিয়ে কাটালাম।
ব্রিটিশ কাউন্সিলে আগাথা ক্রিস্টির যত বই ছিল সব পড়ে ফেললাম। অনেকগুলো বুঝিও নাই। আরো কিছু বই পড়তে শুরু করলাম। তবে, সবচেয়ে মজার ঘটনাটি ঘটেছে একদিন। গিয়ে দেখি লাইব্রেরি বন্ধ। কী করি। ভাবলাম অন্যদিকে হেটে যাই। একটু এগুতে দেখি আর একটা দোতলা বাড়ি। ছোট্ট একটা সিড়ি দিয়ে কেও কেও উপরে যাচ্ছে। আমিও সিড়ি বেয়ে উঠে পড়লাম। আরে এটাও দেখি একটা লাইব্রেরি। থরে থরে সাজানো আছে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ম্যাকমিলানের বই আরো অনেক বই। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে পার্থক্য অনেক বাংলা বই। আমি বুঝে গেলাম বুয়েটে ক্লাস শুরু হতে যদি দেরিও হয় আমার কোন ক্ষতি নাই।
-বাস ততক্ষণে কুমিল্লা পার হয়ে গেছে। হাইওয়ে রেস্টোরেন্ট বলতে তখন বিরতি। তবে, সেখানে গাড়ি দাড়ালো না। তবে, গাড়ি একবার দাড়ালো চৌদ্দগ্রামের কাছে। আমি তখন একটা ঘোরের মধ্যে। কেবল মনে হচ্ছে বুয়েট ছেড়ে এসেছি? কাজটা কী ঠিক হচ্ছে?সব জায়গায় ক্লাস শুরু হয়েগেছে। আলীরা সেকেন্ড ইয়ারে উঠে গেছে। এমন কি, পরের ইন্টারের ছেলে-মেয়েদেরও বুয়েট-মেডিকেল পরীক্ষা শেষ। আমাকে পড়তে হলে পড়তে হবে পাসকোর্সে বিএ। কাজটা কী ঠিক হবে? সবাই কী আমাকে নিয়ে বেশি হাসাহাসি করবে? বুয়েটেই যদি ফেরৎ যাই তাহরে বড়জোড় চারবছরের কোর্স শেষ করতে সালাম ভাই-এর মতো কয়েকবছর বেশি লাগবে? কিন্তু বুয়েট তো বলতে পারবো। যতদিন পাস করতে পারবো না ততদিন টিউশনি করতে পারবো? আমার কী হবে?
গাড়ি যখন আবার চলতে শুরু করলো তখন চোখে কিছুটা ঘুম আসি আসি। ঘোরের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটি কমনীয় মুখ! হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।আচছা ও কী বলে? বলছে বুয়েট না পরলে আর পাত্তা দিবে না? কিন্তু আমি কি তাকে কখনো বলেছি তার হাসিটা আমার হতে পারে?একিদন তাকে নিয়ে ভোরের আকাশে খালি চোখে ধুমকেতু দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। ধুর ছাই, আমি কী জানি কোথায় খুঁজতে হবে!!! কিন্তু তখনো কি আমি ধুমকেতু দেখেছিলাম না তাকে?
চৌদ্দগ্রাম থেকে গাড়ি যতই চট্টগ্রামের দিকে এগোলো ততই আমার চোখের সামনে কেবল তারই ছবি!!!
৯.
গাড়ি যখন শুভপুর ব্রিজের কাছে তখনই আমার ঘোরটা কেটে গেল। বুঝলাম এই সেই ব্রিজ। ১৯৮১ সালের মে মাসের শেষ ক’দিনে এই ব্রিজই হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের এক অনন্য স্বাক্ষী। সেই সময়ে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নিহত হোন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। চট্টগ্রাম থেকে বিদ্রোহী সেনা সদস্যরা শুভপুর ব্রিজের চট্টগ্রাম প্রান্তে অবস্থান নেয়। আর কুমিল্লা থেকে ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের সৈন্যরা অবস্থান নেয় ব্রিজের অপর প্রান্তে। দুই প্রান্তেই যুদ্ধাবস্থা। পরে যখন চট্টগ্রামের বিদ্রোহীরা বুঝতে পারে ঢাকা থেকে যাদের তাদের দলে যোগ দেওয়ার কথা তারা ভোল পাল্টেছে তখন থেকেই এই ব্রিজের দৃশ্য পাল্টাতে থাকে। এই এক বিরাট কাহিনী। এখন না বললে চলে।
ব্রিজ পার হতে হতে আমার ঘোর পুরোই কেটে গেল এবং মায়ের কথা মনে হতে শুরু করলো। আমার মা আমার নানার পাঁচ মেয়ের মধ্যে চতুর্থ। আমার নানা, এই বঙ্গদেশের প্রথম মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট, ১৯২৭ সালে গান্ধীর রেঙ্গুন সফরের সময় আবদুল বারী চৌধুরীর জাহাজ থেকে ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, সেই নানা তাঁর এই মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী ছিলেন না। তাঁর ধারণা ছিল, আমার মা শুকনা বলে, সন্তান হওয়ার সময় মারা যাবে। এই ভয়ে তিনি যে কোন প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতেন। পরে আমার দাদী, দি ফিল্ড মার্শাল অব রাউজান হাজি বাড়ি, আমার নানীকে ম্যানেজ করে আমার বাবা-মা’র বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।
আমার সেই মা, নানী আর নানার কারণে ছোটবেলা থেকেই খালি পড়তেন। আমার বুদ্ধি হওয়ার পর আমি দেখেছি মা সন্ধ্যা থেকেই কিছু না কিছু পড়ছেন। মা ১৯৬২-৬৩ সালে ময়মনসিংহের রাজবাড়িতে মেয়েদের টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বিএড করেন। সেসময় চট্টগ্রাম থেকে ময়মনসিংহ যেতে ক’দিন লাগতো?
তার আগে কিছুদিন অপর্ণা চরণ স্কুলে মাস্টারী করেন। বিএড করে আসার পর যোগ দেন ডা. খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই অবসর নেওয়া। মা’র পড়ার অভ্যাসই আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। বাসার নানান জায়গায় নানান রকমের বই পড়ে থাকতো। মা’র এই অভ্যাসের সঙ্গে দ্যোতনা ছিল দাদা শিক্ষাবিদ আহমদ চৌধুরীর পড়া আর পড়ানোর অভ্যাস। কাজে, আমাদের বাসার আলাপ আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে থাকতো পড়ালেখা সংক্রান্ত নানান বিষয়। যেমন আজকের পত্রিকার কোন লেখাটার কী গুন, আনন্দ মেলার কোন গল্পটা কেমন এই সব।
বাবার একটা বই-এর আলমিরা ছিল। সেই আলমিরাতে কেরি সাহেবের মুন্সী, শরৎ রচনাবলী থেকে শুরু করে কুয়াশাও ছিল। আমার এখনো মনে আছে কুয়াশা-৩ এর প্রচ্ছদে এক মিশরীয় নৃত্যশিল্পীর ছবি ছিল। তাই প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটি বোধহয় বড়দের বই। কিন্তু পড়তে পড়তে দেখা গেল আমিও পড়তে পারি (আমি তখন ফোর বা ফাইফে পড়ি)। সিক্স থেকে আমরা পড়তে শিখে গেলাম কাজী আনোয়ার হোসেনের মাসুদ রানা। সেই সময় খোঁজ পাই রাইফেল ক্লাবের সামনে থেকে বই ভাড়া নেওয়া যায়। ৫০ পয়সা দিলে একটা বই পড়া যায়।
তো, বই পড়া, কিংবা সিনেমা দেখার জন্য যত টাকা-পয়সা দরকার সব কোথায় পাবো? কোন বাবা-মা ছেলেকে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখার টাকা দেন? দেন না। খালি আমার মা দেন। মা বলতেন – যেখানেই যাবি মাগরিবের আজানের আগে বাসায় ফিরবি, কোথায় যাচ্ছিস আমাকে বলে যাবি এবং টাকা পয়সা লাগলে নিয়ে যাবি। কাজে সিনেমা দেখার জন্য টাকা পয়সার কোন অভাব হয়নি। এডমিরাল ইয়ামামাটো দেখেছি বন্ধুদের সঙ্গে, বড় মামা আমাদের সবাইকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্যা ব্রিজ অন দি রিভার কাওয়াই। এই সব সিনেমা দেখতাম আর বাবা-মার কাছে শুনতাম উত্তম-সুচিত্রার সিনেমার কথা। বাবার কাছে শুনেছি তিনি ১৭ বার সাগরিকা দেখেছিলেন। এবং একদিন সব শো’ই দেখেছিলেন। বাবার থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে ১৯৮১ সালে, সার্কের উদ্বোধনের সময় আমি খালার বাসাতে এসে সারাদিনে দেখেছি – মর্নিং-এ জোনাকি সিনেমা হলে শ্যামলী (উত্তম কুমার), ম্যাটিনিতে আনন্দ সিনেমা হলে সোল ভা সাল (দেবানন্দ), সেখান থেকে বাসায় গিয়ে শুনলাম টেলিভিশনে পাশের বাড়ি (কিশোর কুমার – মেরে সামনে ওয়ালি খিড়কি মে) দেখাবে। সেটা শেষ হল সাড়ে আটটার সময়। ফোন করলাম কাকরাইলের সিনেমা হলে। বললাম নাইট শো’র টিকেট আছে কিনা। এবং দেখলাম “সাগরিকা”।
এবং দেখা গেল বাপ-ছেলের পছন্দের ডায়ালগ সেইম–চিনি ক’চামচ?-চিনি? লাগবে না। ঔ সুন্দর হাত দিয়ে নেড়ে দেন। তাতেই মিষ্টি হয়ে যাবে।
তো, এই আমার মা, আমার নানার অতি আদরের মেয়ে, গান গাওয়ার শখ। কলেজে পড়ার সময় গাইতেন – কাজলা দিদি আর নদী আপন বেগে পাগল পাড়া, ছেলেরা কাজলা দিদি বলে ক্ষেপাতো (এই ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টুটি ছিলেন মুহম্মদ ইউনুস, রাজা মিয়া সওদাগরের জুয়েলারি শপের অন্যতম জুয়েল), সেই মা এসে পড়েন আমার বাবাদের রক্ষণশীল ফ্যামিলিতে। ৪ দেবর আর দুই ননদ !!! কিছুদিনের মধ্যে মা’র হারমোনিয়াম নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মা পড়ার অভ্যাসটা ধরে রাখলেন। আর আমাদের মধ্যে সেটি সঞ্চারিত করেছেন। কোনদিন এমনকি আমাদের কোন বকাও দিতেন না। ১৯৭০ সালে আমার বাবা জার্মানী থেকে একটা টেলিভিশন এনেছিলেন। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম কেন্দ্র চালু হওয়ার পর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়ম করে টেলিভিশন দেখাটা হয় আমাদের হবি। কেও আপত্তি করে না। সেই সময় দেখে ফেলেছি হাওয়াই ফাইফ-ও, টারজান, দি ম্যান ফ্রম ইউএনসিএলই, দি ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়েস্টসহ সব বিখ্যাত মুভি। প্রতি শনিবার দেখানো হত চমৎকার সব সিনেমা। দি সাউন্ড অব মিউজিক, দি ক্রেনস আর ফ্লাইং, অপুর সংসার, ব্যালাড ফর ও সোলজার- কী নয়। এবং সব কিছু দেখতে পারতাম মা’র প্রশ্রয়ে। গাড়ি যতই চিটাগাং-এর দিকে আসছিল ততই আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি বুয়েট থেকে না পড়েই ফেরৎ আসি তাহলে সব দোষ হবে আমার মা’র। সবাই মাকে বলবে – আশকারা দিয়ে দিয়ে ছেলেকে মাথায় তুলেছো। এখন বোঝ?বাবা বলবেন – আমি তো আগেই বলেছি। তুমি ডাক্তারী পড়। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার দরকার নাই।খবর পেয়ে আমার চাচা (ততদিনে পাকশী বদলি হয়েছেন, ইঞ্জিনিয়ার বলে ছোটবেলায় ইনি চাচা ডাকতাম) এসে বোঝানোর চেষ্টা করবেন – তুমি পারবা। আবার ফেরৎ যাও। কিন্তু ঠিকই মা’কে কথা শুনিয়ে যাবেন। সবাই বলবে ছেলে মানুষ করার ব্যাপারে আমার মায়ের যে তত্ত্ব সেটা মোটেই ঠিক নয়। ছেলেদের মাইরের ওপর রাখতে হয়। মাইরের নাম লহ্মীকান্ত! যদি ছোটবেলা থেকে মা আমারে মাইরের ওপর রাখতো তাহলে আজকে আমার এই ভিমরতি হতো না।আমি বুঝলাম, আমার নিজের জীবনের সহজতার জন্য আমি যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি তা আমাদের বাড়িতে আমার মা’র অবস্থানকে একেবারে শূণ্য করে দেবে। আমার আদরের মা’কে সবাই গঞ্জনা দেবে আমার কারনে। এটি কী আমি পারবো?
মা খুব সকাল বেলায় বাসা থেকে বের হয়ে যান। কিন্তু ঐদিন রূপালীর বাস অনেক আগেই চাটগাঁ পৌছে গেল (তখন ডাকা চট্টগ্রাম ১৭ ঘন্টা লাগতো না!)। আমিযখন বাসায় ঢুকি তখন মা রেডি হয়ে স্কুলে যাচ্ছিলেন। আমি মা’কে জড়িয়ে ধরলাম। মা জানতে চাইল – কীরে? ভার্সিটি বন্ধ?
-জী। দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ হয়েছে। আমি তোমাদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে এসেছি।
পাদটীকা : ১৯৫০ এর দশকে বিউটি বোর্ডিং-এর কবিরা অগত্যা নামে একটি মাসিক সাময়িকী প্রকাশ করতেন। সম্পাদক ছিলেন সম্ভবত ফজলে লোহানী। সেখানে একবার কোন এক কবির (সৈয়দ শামসুল হক?) একটি ধারাবাহিক উপন্যাস ছাপা হচ্ছিল। তো, এক পর্ব শেষ হলে যেখানে রাত হয়ে গেছে দেখে নায়িকাকে নায়কের বাসায় রাত কাটাতে হবে। এই জন্য মশারী -টশারী ইত্যাদি খোজাখুজি করছে নায়ক। কিন্তু পরের পর্ব শুরু হল নায়কের বাসায় সকালে নায়ক নায়িকা চা খাচ্ছে এই দুশ্য থেকে। তখন অনেক পাঠক চিঠি লিখে মধ্যবর্তী সময়ে কী হয়েছিল সেটি জানতে চান। তখন পরের পর্বে সম্পাদক উপন্যাসের শুরুতে একটি ঘোষণা দিলেন-
সম্পাদক দায়ী নহেন
এই উপন্যাসের আগের আগের পর্বের শেষ এবং আগের পর্বের শুরু মাঝখানে যা কিছু ঘটুক না কেন, তার জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।
১০
কী মুনির মিয়া, এসে পড়লা দেখছি!
আহসানউল্লাহ হলের গেটের সামনে রিকসা থেকে নামতে দেখা হয়ে গেল রুমি ভাই-এর সঙ্গে। তিনি সম্ভবত বন্ধে বাড়ি যান নাই। আমাকে দেখে ব্যাগ নেওয়ার সহায়তা করলেন।
কী বলবো, বুঝতে পারছি না। তাই চুপ থেকে রুমি ভাই-এর সঙ্গে হেটে ১২৭ নম্বর রুমের সামনে গেলাম। মনে হচ্ছে রুমমেটরা কেও ফিরে নাই। ব্যাগ রেখে হাত-মুখ ধুতে গেলাম। রুমি ভাই দাড়িয়ে আছে।
‘চল, তোমাকে চা খাওয়াই।”
আমি আর রুমি ভাই আহসান উল্লাহ হলের কেন্টিনের দিকে হাটা দিলাম। পথেই দেখা হয়ে গেল রুমি ভাই-এর রুমমেট। ওনাকে আমি আগেই খেয়াল করেছি। তবে, কথাবার্তা খুব একটা হয়নি। রাফু ভাই (স্থপতি কাজি আনিস উদ্দিন ইকবাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিল্ডিং ফর ফিউচার) আমাকে দেখে হাসলেন। বললেন – কি, ফিরে আসলা তাইলা?
বুঝলাম রুমি ভাই আমার না ফেরার প্রত্যয় জনে জনে বলে ফেলেছেন। কী আর করা।
কেন্টিনে বসে রুমি ভাইকে বললাম – আমার ফিরে আসাতে আপনি মোটেই অবাক হোননি। আর যদি জানতেন যে আমি ফিরবো তাহলে তখন বললেন না কেন। আমার প্রায় কান্না পাচ্ছে!
“দুইটি কারণ। প্রথমত আমি চেয়েছি তুমি নিজের বোধে ফেরৎ আসো। আর আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, তুমি ফিরবা কারণ তোমার মত আমিও দুই সপ্তাহ পর বুয়েট থেকে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু জলেশ্বরীতলা যাওয়ার আগেই বুঝে ফেলেছিলাম আমার কোন বিকল্প নাই।”
যাক, আমি তাহলে একা না।
চা খেতে খেতে রুমি ভাই যে কথাগুলো বলেছিলেন তার বেশিরভাগই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী। আমাদের বেঁচে থাকা যে একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব সেটা আমি সেদিনই অনেকখানি বুঝে ফেলেছিলাম। তবে, সবচেয়ে বেশি বুঝেছিলাম – নিজের কাজটা করে যাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় এবাদত, সর্বোত্তম প্রত্যয়। ফলাফল নিয়ে ভাবার কিছু নাই। প্রাণপণ এবং সর্বোচ্চ চেষ্টায় যা হবে সেটাই ফলাফল।
রুমি ভাই আমাকে রুমে রেখে যাওয়ার সময় একটা আপ্ত বাক্য বলে গেলেন। পরে জেনেছি এটা ‘চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান’ কমরেড মাও সে তুং-এর একটা বিখ্যাত বানী
পড়, পড় এবং পড়!
তো, আমি বুঝে গেলাম আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করে বুয়েটে ফেল করতে পারবো, হলের অন্যান্য আদু ভাই-দের মতো হতে পারবো কিন্তু তার চেয়ে খারাপ হতে পারবো না। অন্যদিকে পড় পড়ে আমি যদি নতুন একটা জগৎ বানিয়ে ফেলতে পারি তখন আমার নিজেরই একটা জগৎ হয়ে যাবে। তখন আমাকে কে ঠেকাবে?
এর কয়েকদিন পর, হলের কমন রুমের পাশের রুমটা খোলা দেখে সেখানে উকি মারতে দেখি সেখানে সারি সারি আলমিরা আর আলমিরা ভর্তি বই। একজন দাড়িওয়ালা চাচা মতোন (নামটা মনে নেই) বসে আছেন। তার কাছ থেকে জানলাম এটি “হল লাইব্রেরি।”
কেন যে আগে দেখলাম না।
দেখলাম আমার সব স্বপ্নের বই সেখানে।
নাম শুনেছি কিন্তু কোনদিন পড়তে পারি নাই এমন একটা চরিত্র হর্ষবর্ধন। দীর্ধদিন ধরে জেনেছি “চক্কোরবরতীরা কঞ্জুষ হয়”। কিন্তু চট্টগ্রামে কারো বাসাতে কোনদিন শিবরামের কোন বই দেখি নাই। কিরিটি রায়ের যে অমনিবাস আছে সেটাই তো জানতামই না। রবীন্দ্র রচনাবলী একটা বাসাতে ছিল। কিন্তু মানিক বন্দোপাধ্যায়ের রচনাবলী? কবর ছাড়াও মেট্রিকের ব্যাকরণ বই-এর রচয়িতা মুনির চৌধুরীর যে আরো বই আছে সেটাই বা কে জানতো।
চাঁদে অমাবস্যা নামে লাল-শালুর লেখকের একটা বইও সেখানে আছে। সেটি পড়ার পর এতো আপ্লুত হলাম যে, কয়েকদিন ধরে কিছুই মাথায় ঢুকলো না। আমার অবস্থা দেখে রুমি ভাই বললেন – আরে চাঁদে অমাবস্যাতে এই অবস্থা। আউটসাইডারে তোমার কী হবে?
আউটসাইডার? আলবেয়ার কামু? ম্যাকিয়াভেলির প্রিন্স? সামুয়লেসনের ইকোনমিক্স? চানক্যের অর্থশাস্ত্র?
এসবের মানে কি। এতসব বই আমি কেমনে পড়বো? সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং এর মত জটিল বিষয়!
কী হবে অতো ভেবে। বরং আমি পড়তে শুরু করি।
এর মধ্য রুমি ভাই একদনি খবর দিলেন ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে আরো একটা লাইব্রেরি আছ-সিডিএল। ওতো দূরে যাওয়ার সামর্থ কেমনে হবে। হল থেকে হেটে সায়েন্স ল্যাব। তারপর বাস শংকর। মেম্বার হয়ে আসলাম।
শুরু হল আমার নতুন জগতের কাজ। মুজতবা আলী আদ্রে জিঁদের কথা কেন বলেছিলেন সেটা বুঝতে শুরু করেছি। আর এর পর একদিন জানতে পারি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের কথা। এই নোটের প্রথম পর্বে রয়েছে সেই কথা।
ততদিনে বুঝে ফেলেছি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস না করলেও জগত বানাতে আমার কস্ট হবে না।
ক্লাস টেস্ট কিংবা সেমিস্টার পরীক্ষা আসুক।
আসুক পরীক্ষা। পরীক্ষারে আর ডরাই না।
[২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে ১০ পর্বের এই সিরিজটা লিখেছিলাম ফেসবুকে, নোটাকারে। নিজের সাইটে এনে রাখলাম দুইটা কারণে- যাতে চট করে পাওয়া যায়। আর একটা হল পরের এপিসোডগুলো লেখার একটা তাড়া থাকে]