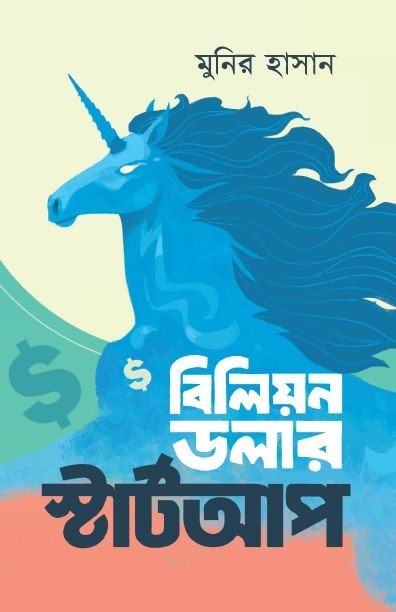গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য : শরিয়তপুরের উপেক্ষিত প্রকৃতি বিজ্ঞানী
 ছোট্ট মৎসকুমারীর কথা মনে আছে?
ছোট্ট মৎসকুমারীর কথা মনে আছে?
ঐ যে একদিন সে দেখেছে রাজকুমারকে এবং তারপর সে মানুষের মত দু’টো পা চেয়েছিল?
হ্যা। আমি হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের বিখ্যাত রূপকথা “লিটল মারমেইডের” কথা বলছি। ওখানে মৎসকুমারীর লেজ খসে গিয়ে পা হয়ে ছিল! কিন্তু প্রকৃতিতে বিশেষ করে প্রাণিজগতে কিন্ত এমনটা সহসা হয় না। হাতির বাচ্চা কিন্তু একটা ছোট হাতিই। মানে তার হাত, পা, শুড় সবই থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু আনুপাতিক হারে বাড়ে। মানুষের বেলায়ও তাই।
কোন ব্যতিক্রম কি তোমার মনে পড়ে? চোখ বন্ধ করে একটু ভাববে?
হ্যা। ধরে ফেলেছ নিশ্চয়ই। ব্যাঙ। ছোট বেলার ব্যাঙ হলো ব্যাঙাচি, লেজ থাকে, কানকো থাকে। কিন্তু ব্যাঙ হতে হতে লেজ খসে পড়ে, জন্মায় পা। প্রকৃতির এই বিরল ঘটনাটি মানুষ প্রথম থেকে লক্ষ করেছে। তবে, কেও কিন্তু ভাবে নি, আচ্ছা, কী করলে ব্যাঙাচি আর ব্যাঙ হতে পারবে না? বড় ব্যাঙ্গাচিই রয়ে যাবে?
শরিয়তপুর জেলায় জন্ম এরকম একজন বাঙ্গালি প্রকৃতিবিদ গোপাল চন্দ্র ভটাচার্য প্রথম এমনটা ভাবলেন। তিনি ভাবলেন পরিবেশের যেহেতু একটা প্রভাব আছে জীবনের ওপর তাহলে নিশ্চয়ই এখানেও এমন কিছু সম্ভব। ব্যাঙ্হাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তরের মূল কারণ আয়োডিন ঘটিত থাইরক্সিন হরমোন। কিন্তু গোপালবাবু দেখলেন যদি ব্যাঙাচির ওপর পেনিসিলিন প্রয়োগ করা যায় তাহলে আর সেটি ব্যাঙ হয় না, বড় ব্যাঙ্গাচিই থেকে যায়! গোপালবাবু যখন এই গবেষণা করছিলেন তখন কলকাতায় এসেছিলেন বিখ্যাত প্রকৃতিবিদ জুলিয়ান হাক্সলি। উনি খুব অবাক হলেন এবং যাবার সময় বলে গেলেন বিখ্যাত নেচার পত্রিকায় বিষয়টি ছাপিয়ে রাখতে। তা সেটা আর করা হল না!
তো, যে লোকটা এরকম দিনের পর দিন পানির মধ্যে একটি ব্যাঙাচি রেখে পর্যবেক্ষণ করতে পারে তার সে গুন কিন্তু ছোট বেলা থেকেই দেখা যাওয়ার কথা। আজ থেকে প্রায় ১২০ বছর আগে, ১৮৯৫ সালের ১ আগস্ট, আমাদের এখনকার শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার একটি গ্রামে গোপাল চন্দ্র ভটাচার্যের জন্ম। বাবা অম্বিকা চরণ কুরীন ব্রাহ্মণ। পেশা যজমানি। মানে তিনি বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে পূজা-পার্বন করে দেন। মা শশীমুখী। গোপাল বড় ছেলে এবং তারপর তাদের আরো চারটি ছেলে-মেয়ে হয়। কিন্তু গোপালের পাঁচ বছর বয়সেই তাঁর বাবা মারা যান। বেচারি শশীবালা নিদারণ অর্থকস্টে ছেলেমেযেদের মানুষ করার চেষ্টা করেন। বড় ছেলে হিসাবে সে কাজে গোপালকে জড়িয়ে পড়তে হয়। এর মধ্যে গ্রামের পাঠশালায় পড়ে গোপালচন্দ্র ভর্তি হোন লোনসিং বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৯১৩ সালে মেট্রিক পাশ। তারপর ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে আইএ ক্লাশে ভর্তি। কিন্তু কয়েকদিন পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ফলাফল গোপাল চন্দ্রের আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার ইতি।
গ্রাম ফিরে গিয়ে তিনি ভূগোলের শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ঐ লোনসিং বিদ্যালয়ে। ছোটবেলা থেকে জলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর একটা নেশা তাঁর ছিল। তবে, গাছগাছালি থেকে তাঁকে বেশি টানতো পোকা-মাকড়। পিপড়া, মাকড়শা, গুবরে পোকা এগুলো ধরে ধরে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন। যোগেন নামে তাঁর একজন সহকর্মী ছিলেন ঔ স্কুলে। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর একটি বইতে লিখেছেন, “মাঝে মাঝে যোগেন মাস্টার ছেলেদের ডেকে এনে ম্যাজিকের খেলা দেখাতেন। একটা মজার জিনিস দেখাবেন বলে একদিন তিনি সবাইকে ডেকে নিয়ে এলেন। পকেট থেকে গাঢ় খেয়রি রঙের কতকগুলি বিচি বের করে টেবিলের ওপরে রাখার পরেই একটি বিচি প্রায় চার ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠল। তারপর এদিক-ওদিক থেকে প্রায় সবগুলি থেকে থেকে লাফাতে শুরু করে দিল।…অবশেষ মাস্টার মশাই ছুরি দিয়ে একটা বিচি চিড়ো ফেলতেই দেখা গেল তার ভেতরে একটা পোকা (লারভা)”।
এই ঘটনা তাঁকে আরো বেশি পোকা-মাকড়ের প্রতু আকৃষ্ট করে তোলে। পাশাপাশি তিনি প্রকৃতির অন্যান্য ঘটনাবলী বিমেষ করে প্রচলিত ভৌতিক বিষয়ও তলিযে দেখার সিদ্ধান্ত নেন। সে সময় রাতের বেলায় গ্রামের জল-জঙ্গলের ধারে হটাৎ হটাৎ আলো দেখা যেত- আলেয়া। লোক বলতো -ভুতের আগুন। তো, ভুত দেখার লোভে গোপাল চন্দ্র একদিন এক বন্ধুকে নিয়ে রাতের বেলা রওনা দিলেন আলেয়া দেখার জন্য।
লক্ষ্য “পাঁচীর মার ভিটা”। অবমাবস্যার রাত। গা ছম ছম ব্যাপার। একদিন ভূতের আলো দেখার জন্য দুই বন্ধু মিলে রাতের আধারে গিয়েছিলেন ‘পাঁচীর মার ভিটা’ নামক একটি স্থানে।
সেদিনও বৃষ্টি হচ্ছে হাতে হারিকেন, ছাতা এবং ম্যাচ। ঝোপ ঝাড়া পেড়িয়ে পৌছলেন ভিটার কাছে। হারিকেনটা একটু কমিয়ে অল্প কিছুক্ষন অপেক্ষা করতেই দেখলেন অস্পষ্ট আলো।সাহস করে আর একটু কাছে যেতেই দপ করে জ্বলে উঠল। কিছুটা লাফা লাফি করে এবার যেন স্থির হলো। আরও একটা সাহস করে সামনে এগুতেই দেখলেন আগুনের কুন্ডলী কিন্তু আশ্চার্য ব্যাপার আগুনের কোন শিখা নেই। কয়লা পুরলে যেমন আগুন হয় তেমন জ্বল জ্বল করছে। আলোটার তীব্রতা নেই কিছুটা নীলাভ। এই আলোতে চারপাশের কিছু অংশের ঘাস লতা পাতা ভালই দেখা যাচ্ছে। আরো কাছে যেতেই দেখলেন পুরনো একটা গাছের গুড়ি থেকে আলো নির্গত হচ্ছে। গুড়ির কাছেই একটা কচু গাছ এর পাতা এ দিক ও দিক দুল খাচ্ছে। এই পাতাটার জন্যই দেখা যাচ্ছিল আলোটা একবার নিবছে আবার জ্বলছে। তিনি গাছের গোড়া থেকে কিছুটা অংশ সংগ্রহ করে নিয়ে আসলেন। পরে বুঝলেন আসলে জমে থাকা জৈব পদার্থ পচে মিতেন গ্যাসে পরিণত হয় আর সেটিই বাতাসের সংস্পর্শে জ্বিলে ওঠে। এই হলো ভুতের আলো।
গ্রামে বেশিদিন থাকা সম্ভব হলো না আর্তিক সংকটের কারনে। পাড়ি জমারেন কোলকাতায়। চাকরি নিলেন কাশিপুরে অবস্থিত বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে স্কুলের কথা মনে করতেন। পোকামাকড়ের ঘরবসতি নিয়ে ভাবতেন। কলকাতার বাসার আশে পাশে মাকড়সা, পিপড়া এগুলো দেখাও অব্যাহত রাখলেন। এর মাঝে একদিন লিখে ফেললেন আলোয়া নিয়ে তার পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত। পাঠিয়ে দিলেন “প্রবাসী” পত্রিকায়। প্রবাসী পত্রিকায় গোপালচন্দ্রের নিবন্ধ চোখে পড়লো আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর। জগদীশ চন্দ্র বসু তখন মাত্র বসু মান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। খুঁজে ফিরছেন তাদেরকে যাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ভাল। জগদীশচন্দ্র বসুর আগ্রহে ১৯২১ সালে গোপাল চন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দেন। তখন থেকে তার গবেষণার প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে যায়।
সেই বছরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আসেন জার্মান প্রকৃতি বিজ্ঞানী হ্যানস মলিশ। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেওয়া হয় তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্য। ছয় মাসের এই কাজের ফলে প্রকৃতি ও প্রাণি পর্যবেক্ষণের কাঠামোগত ব্যাপারটিও তিনি রপ্ত করে ফেলেন। দুইজন মিলে কীটপতঙ্গের আচার-আচরণ, গতি-প্রকৃতি, খাদ্য সংগ্রহের কৌশল, তাদের বংশবিস্তার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমন্ধে গবেষণা করেন। যার ফলে কীটপতঙ্গ ও লতাপাতা বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা আরও বৃদ্ধি পায়। সহকারি হিসাবে তার একটি কাজ ছিল ছবি আকা। সেটিতেও তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু তখন তাঁকে ছবি তোলা মিখতে বলেন এবং পরে কিছুদিন তিনি আচার্যের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের ওপরও একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করেন। সহায়তা করতে করতে একদিন তিনি নিজেও একা একা গবেষণা করতে শুরু করেন।
বনু বিজআন মন্দিরে থাকতে গোপালচন্দ্র নালসো পিপড়ে (লাল পিপড়ে নামে পরিচিত) নিয়ে ব্যাপক গবেসণা করেন। তিনি পিপিড়েদের কলোনীকে স্বচ্ছ সেলোফেন দিযে ঢেকে রাখলেন আর দিনের পর দিন সেগুলোর আচরণ লক্ষ করলেন। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ তিনি প্রকাশ করেন ১৯৪০ সালে যেখানে তিনি দেখান পিপড়েদের খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে তাদের যথাক্রমে রাজা, রানি, কর্মী ও সৈনিক পিপড়ে হওয়ার সম্পর্ক আছে। সে সময় ধারণা ছিলে জিনই মনে হয় একমাত্র কারণ। কিন্তু গোপালচন্দ্রের গবেসণায় বোঝা গেল না, জিনগত কারণ ছাড়াও খাত্যাভাসও পিপড়ের শ্রেণীভেদের একটা অন্যতম কারণ। গোপালচন্দ্রের এই আবিস্কারে চার দশক পরে ১৯৮০ সালে দুজন পিপড়ে বিশেষজ্ঞ একই বিষয় আবিস্কার করেন। কিন্তু গোপালচন্দ্র তাঁর যথাযথ স্বীকৃতি পাননি।
কীট পতঙ্গের জগতে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারটা কম, সহজাত প্রবৃত্তি বেশি। কিন্তু গোপাল চন্দ্র আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন এক ধরণের কুমরো পোকা কানকোটারির ব্যবহার। অন্যান্য পোকার মত এরাও তাদের ডিম রক্ষা করার চেষ্টা করে তবে সেজন্য তারা কেবল সহজাত প্রবৃত্তিতে চালিত হয় না। কানকোটারি তাদের পায়ের মধ্যে কাঁদা লাগিয়ে নেয়। তারপর কাঁদাগুলো শুকিযে গেলে সেটি মক্ত হযে যায। এ যেন পায়ে ‘শক্ত বুট” পড়া। তারপর কোন শত্রু ডিমের কাছে আসলে তাকে এই বুট পড়া পা দিয়ে লাথি দিয়ে দেয় কানকোটারি!!!
বসু বিজ্ঞান মন্দিরে থাকাকালীন সময়ে গোপালচন্দ্র গবেষণা করেছেন বিভিন্ন ধরনের পোকা মাকড় নিয়ে। তার মধ্যে ব্যাঙ্গাচি, শুইপোকা, মাছখোকো মাকড়াশা, বোলতা ইত্যাদি পোকা মাকড়ের জীবন ও বৈচিত্র। স্ত্রী ও পুরুষ মাকড়সার আচার আচরণ ও গতিবিধি, তাদের শক্তি ও অবস্থান, ডিম দেয়া ও এর যত্ন, স্ত্রী মাকড়াসার প্রতি পুরুষ মাকড়াসার আচরণ, স্ত্রী মাকড়সা কর্তৃক পুরুষ মাকড়সার গলাধঃকরণ। শুয়োপোকা, প্রজাপতি, পিঁপড়ে ইত্যাদির জীবন রহস্য । এ সময় তিনি কীটপতঙ্গ ও লাতাপাতা বিষয়ে ১৬ টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন। এগুলোর বেশিরভাগ প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। তার লেখা কিছু ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির মুখপত্র, মডার্ন রিভিউ ইত্যাদি বিখ্যাত পত্রিকায়। বাংলার “পিপীলিকা অনুকারী মাকড়সা“প্রবন্ধে একটি নতুন প্রজাতীর লাল পিঁপড়ে অনুকারী মাকড়সার নিজের মেয়ের নামে নামকরন করেন “Propostira ranii”। (“রানী” গোপাল চন্দ্রের একমাত্র কন্যার নাম)। পিঁপড়া,মাকড়সা,ব্যাঙ্গাচি এবং ফড়িং এর উপর অনেক ছবি তুলেন। তাঁর প্রায় ২২টির মতো নিবন্ধ ইংরেজীতে প্রকাশ পায়।
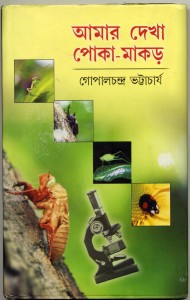 ১৯৪৯ সালে গোপাল চন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির ছেড়ে চলে আসেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে। দায়িত্ব নেন এর মুখপত্র, বিজ্ঞান সাময়িকী জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার। ১৯৫১ সালে ভারতের কীট-পতঙ্গের উপরে নিবন্ধ পাঠের জন্য প্যারিসে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক সভায় আমন্ত্রন করা হয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো সেখানে তার একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার কারনে তাকে উপেক্ষা করা হলে তিনি মনো:কস্ট পান। অথচ ১৯৪০ সালের আগেই গোপাল চন্দ্র প্রকৃতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠেন।
১৯৪৯ সালে গোপাল চন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির ছেড়ে চলে আসেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে। দায়িত্ব নেন এর মুখপত্র, বিজ্ঞান সাময়িকী জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার। ১৯৫১ সালে ভারতের কীট-পতঙ্গের উপরে নিবন্ধ পাঠের জন্য প্যারিসে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক সভায় আমন্ত্রন করা হয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো সেখানে তার একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার কারনে তাকে উপেক্ষা করা হলে তিনি মনো:কস্ট পান। অথচ ১৯৪০ সালের আগেই গোপাল চন্দ্র প্রকৃতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠেন।
“করে দেখা” নামে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের তিন খন্ডে একটি বিখ্যাত বই রয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন তিনি শিশু কিশোরদের উপযোগী করে প্রায় ৮০০-এর মত নিবন্ধ লিখেন। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে পৌছে দেওয়ার এই কাজের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি ১৯৬৮ সালে লাভ করেন ‘আনন্দ পুরুস্কার’। ১৯৭৪ সালে লাভ করেন আচার্য সতেন্দ্রনাথ বসু ফলক। ১৯৭৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তাকে দেওয়া হয় জাতীয় সংবর্ধনা। ১৯৭৫ সালে ‘কীটপতঙ্গ’ গ্রন্থের জন্য তিনি পান রবীন্দ্র পুরস্কার।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮১ সালের ২১ জানুয়ারী তাকে সম্পমানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত করে।
১৯৮১ সালের ৮ এপ্রিল গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।